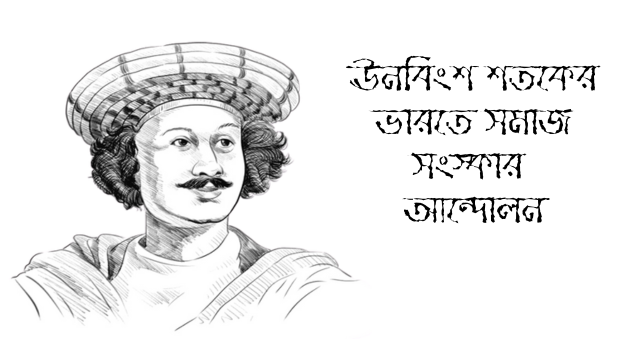Q. ঊনবিংশ শতকের ভারতে সমাজ সংস্কার আন্দোলনগুলির প্রকৃতি ও তাদের সীমিত সাফল্য সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
❐ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের ফলে জনসমাজে এক নতুন চেতনার উন্মেষ হয়। এই নতুন চেতনার প্রধান বৈশিষ্টগুলি ছিল যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। এই নতুন চেতনা উনবিংশ শতকে ভারতে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করে দেয়। সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের পুরোধার স্থান যিনি গ্রহণ করেন তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন যেমন পঙ্কিলতায় নিম্মজিত সনাতন হিন্দু ধর্মকে সংস্কার করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন, তেমনি সামাজিক কুসংস্কারগুলি দূর করতে বদ্ধ পরিকর হন। তবে এখানে উল্লেখ্য যে ভারতের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন কিন্তু সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে ওত প্রোত ভাবে জড়িত ছিল।
✽ উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন : হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিল। রামমোহন, ডিরোজিওর হাত ধরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, অ্যানি বেসান্তের প্রমুখের প্রচেষ্টায় দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা তথা সমগ্র ভারতে সর্বব্যাপী রূপ পরিগ্রহ করেছিল।
✽ সমাজ সংস্কার আন্দোলনগুলির প্রকৃতি : উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক কুপ্রথাগুলির মূল উৎপাটন করা। যে সামাজিক পীড়া ঊনিশ শতকের মনীষীদের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল নারীজাতির প্রতি অসৎব্যবহার। তারা সতীদাহ, গঙ্গা সাগরে সন্তান বিসর্জন, কন্যা সন্তানদের হত্যা প্রভৃতি কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করতে এবং বিধবা বিবাহ ও পদাপ্রথার অবসান ইত্যাদির জন্য বদ্ধ পরিকর ছিলেন। স্ত্রীলোকের শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে যে সকল বাধা ছিল তা দূর করে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তারা আগ্রহী হন। হিন্দু সমাজের জাতীভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম আরম্ভ করেন এবং নিম্নবর্ণের বিশেষ করে অন্ত্যজদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হন। ঊনবিংশ শতকের আন্দোলন মূলত নারী মুক্তি আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল।
✽ সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন : সতীদাহ নামক এই নিষ্ঠুর অমানবিক প্রথা ধর্মীয় সমর্থন নিয়ে দীর্ঘদিন হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের উপর শাসন কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর দেশীয় প্রজাদের সামাজিক ও আচার অনুষ্ঠান হস্তক্ষেপে নিরুৎসাহী ছিল। তারা সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ভারতীয়দের রুষ্ট করতে চায় নি। আধুনিক ভারতের পথিকৃত রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ সাধনের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর আন্দোলন সফলতা পায় ১৯২৯ খ্রিঃ। এ বছর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক আইনের দ্বারা সতীদাহ প্রথাকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষনা করেন।
হিন্দু বিধবাদের সম্পত্তিতে অধিকার লাভ, সমাজে নারী জাতির মর্যাদাবৃদ্ধি এবং স্ত্রীজাতির শিক্ষার জন্য রামমোহন আন্দোলন চালান। তিনি বর্নাশ্রম ব্যবস্থাকে পরিহার না করলেও জাতিভেদ প্রথার ফলাফলকে নিন্দা করেন। তিনি কৌলিন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর সমাজসংস্কার মূলক কার্যের দায়িত্ব ব্রাহ্মগন ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুরা গ্রহণ করেন। নব্যবঙ্গ সম্প্রদায় (ডিরোজিওর শিষ্যরা) তাদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে নানা সামাজিক বিধিনিষেধ ভঙ্গ করে। তারা সামাজিক কুপ্রথাগুলি ভেঙে ফেলার জন্য যুক্তিবাদের সাহায্য নিয়েছিলেন।
সমাজ সংস্কার ও নারী মুক্তি আন্দোলনে তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই সভা ও পত্রিকা সফল সংস্কারকারী বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে বিধবা বিবাহ ও অসবর্ন বিবাহের সমর্থনে, বহু বিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজেও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে বিশেষ অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিল। কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় ১৮৭২ খ্রিঃ ভারতীয় বিবাহ বিধি আইন প্রবর্তিত হয়েছিল। এর দ্বারা বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। অসবর্ন ও বিধবা বিবাহ স্বীকৃত হয়। ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করে। তারা স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে ও পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছিল।
✽ ইংরেজ সরকারের নীতি : ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত যাতে আরো শক্ত হয় তার জন্য ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণের কিছু প্রচেষ্টা ইংরেজ সরকার গ্রহণ করেছিল। এ প্রসঙ্গে বেন্টিঙ্ক ও ডালহৌসির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমজনের সময় সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন এবং দ্বিতীয় জনের সময় বিধবা বিবাহ আইন প্রনীত হয়েছিল।
✽ বিধবাদের পুনর্বিবাহ আন্দোলন : কোম্পানির শাসনকালে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম একটি বিষয় ছিল বিধবাদের বিবাহ সংক্রান্ত প্রশ্নটি। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত বলে প্রমান করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মসমাজ ও নব্যবঙ্গীয়রা তাঁকে সমর্থন জানান। অন্যদিকে হিন্দুধর্মসভা এর তীব্র বিরোধিতায় নামে। বিদ্যাসগর বুঝতে পারেন সরকারী সাহায্য ছাড়া বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। অবশেষে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা সখলতা পায়। ১৮৫৬ খ্রিঃ সরকার হিন্দু বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ বলে ঘোষণা করে।
✽ স্ত্রীশিক্ষার প্রসার : উনিশ শতকে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই সময়ের সংস্কারকেরা স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের উপর সকলেই জোর দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে প্রথম যিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সমাজের অর্ধ্বংশকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে কখনই গোটা সমাজে আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি খ্রিস্টান মিশনারীদের স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিলেন। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনের স্তরে উন্নীত করেছিলেন। ১৮৪৯ খ্রিঃ বেথুন সাহেবের সঙ্গে বেথুন স্কুল স্থাপন করেন। সরকারী সাহায্য ছাড়াই ৩৫ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এছাড়া ব্রাহ্মসমাজ, নব্যবঙ্গ গোষ্টী, আর্য সমাজ, প্রার্থনা সমাজ ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে যথেষ্ট উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিল। এক কথায় উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারের সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের ভিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। শুধু হিন্দু সমাজ এয়, মুসলমান সমাজে পর্যন্ত রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের মত কিছু আলোকপ্রাপ্তা মহিলা তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন।
✽ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক : ভারতীয় সংস্কারকেরা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও নিজেদের ভারতীয় সত্ত্বাকে বিসর্জন দেন নি। তাদের সুপ্রাচিন অতীত ঐতিহ্যের মহিমারিত জাতীয়তাবাদী আবেদন ছিল সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তারা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের রাজনীতির সঙ্গে কখনই ধর্মসংস্কার আন্দোলনকে যুক্ত করতে চান নি। এককথায় ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতের সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদের মধ্যে কোন বিরোধিতা ছিল না, ছিল না পারস্পরিক দ্বন্দের সম্পর্ক।
✽ সীমিত সাফল্য : ঔপনিবেশিক যুগে অবশ্য এই সমাজ সংস্কার আন্দোলনগুলির কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। সুমিত সরকার রামমোহনকে কিছু সীমাবদ্ধতার জন্য আধুনিক ভারতের প্রবক্তা বলতে রাজী নন। তাঁর মতে, “রামমোহন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পরিধির মধ্যে থেকে সংস্কারের বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন, ঔপনিবেশিক শাসনের মূল কাঠামোকে নির্মূল করতে আগ্রহী ছিলেন না। সতীদাহ প্রথা ছিল একটি সামাজিক সমস্যা। এ কারণে এই প্রথা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভব হয় নি। বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয় দু-একটি বিধবা বিবাহ দিলেও সার্বিকভাবে এই প্রথা সমাজে প্রচলিত হয় নি। বহুদিন পর্যন্ত আইন প্রনয়নের পরও বিধবা বিবাহ দিলে কন্যার পিতা নিন্দিত ও একঘরে হতেন। কিছু স্কুল কলেজ মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও সেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। সর্বোপরি উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের তেমন ভাবে নাড়া দিতে পারে নি। এক কথায় এই আন্দোলনের সাফল্য ছিল সীমিত।
◻︎ উপসংহার : এতসত্বেও বলা যায় উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারকগন ভারতের জনজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। তাদেরই প্রচেষ্টায় মধ্যযুগীয় তমসাচ্ছন্ন ভারতবাসী কুসংস্কার, জড়তা, অনুষ্ঠান সর্বস্বতা ও লোকাচারের বৃত্ত হতে মুক্ত হয়ে নবজীবনের পথ দেখেছিল।
Tags : সমাজ সংস্কার আন্দোলন কি, কয়েকজন সমাজ সংস্কারক এর নাম,