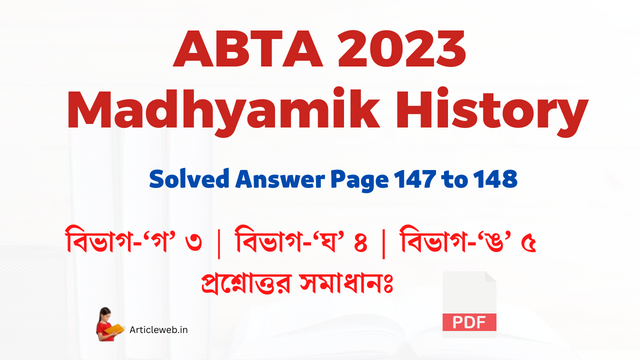ABTA Madhyamik 2023 বিভাগ-‘গ’ ৩ বিভাগ-‘ঘ’ ৪ বিভাগ-‘ঙ’ ৫ প্রশ্নোত্তর সমাধান
❐ আরো পড়ুনঃ 2023 ABTA Madhyamik
{tocify} $title={Table of Contents}
বিভাগ-‘গ’ ৩
বিভাগ-‘গ’ ৩। দুটি বা তিনটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো ১১টি) : ১১×২=২২
৩.১ পরিবেশের ইতিহাসের গুরুত্ব কী?
উত্তরঃ পরিবেশের ইতিহাসের গুরুত্ব হল – [1] মানবসভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে পরিবেশের ভূমিকা চিহ্নিত করে পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। [2] পরিবেশের সংকটজনক পরিস্থিতি, পরিবেশ বিপর্যয় এবং তার ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষকে অবগত করা। সর্বোপরি, বাসস্থানের ওপর পরিবেশগত গুরুত্ব আরোপ করা।
৩.২ সোমপ্রকাশ পত্রিকার বিষয়বস্তু কী ছিল?
উত্তরঃ ঊনবিংশ শতকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকার পাতায় পাতায় আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার নানা উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি তাঁর 'বাঙালা সংবাদপত্রের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, “যাহার আবির্ভাবে ও প্রভাবে সংবাদপত্র মহলে হুলুস্থূল পড়ে, তাহাই ‘সোমপ্রকাশ।” ব্রিটিশ কুশাসনের প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছিল ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকা। এই পত্রিকাটি সমকালীন ভারতীয় আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলির বর্ণনা প্রদান।
৩.৩ “শ্রী রামপুর ত্রয়ী” কাদের বলা হয়?
উত্তরঃ বাংলার হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে ১৮০০ সালে একটি ছাপাখানা গড়ে ওঠে। নাম 'শ্রীরামপুর মিশন প্রেস'। এই প্রেসটি গড়ে তোলেন উইলিয়াম কেরি, উইলিয়াম ওয়ার্ড এবং জোসুয়া মার্শম্যান নামে তিনজন মিশনারি। বাংলার ছাপাখানার ইতিহাসে এঁরা 'শ্রীরামপুর ত্রয়ী' নামে পরিচিত।
৩.৪ ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ সনদ আইনের গুরুত্ব কী?
উত্তরঃ শিক্ষাক্ষেত্রে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদের গুরুত্ব ছিল যে, এর দ্বারা— [1] কোম্পানি প্রতি বছর ১ লক্ষ টাকা ভারতীয় জনশিক্ষার জন্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। [2] ভারতে জনশিক্ষার নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ‘জনশিক্ষা কমিটি’ বা ‘কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন' গঠিত হয়।
৩.৫ খুৎকাঠি প্রথা কী?
উত্তরঃ খুঁৎকাঠি বা খুৎকাঠি প্রথা হলো এক ধরনের ভূমি ব্যবস্থা যা পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশের মুন্ডা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল। খুঁৎকাঠি ব্যবস্থায় জমিতে ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে যৌথ মালিকানা স্বীকৃত ছিল। খুঁৎকাঠি প্রথার অপর নাম কুন্তকট্টি প্রথা। বাংলাদেশে একে উচ্চারণ করা হয় 'খুন্তকাট্টি'।
৩.৬ কোল বিদ্রোহের দুটি কারণ লেখো।
উত্তরঃ (i) রাজস্ব নির্ধারণ : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছোটোনাগপুরের শাসনভার ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে গ্রহণ করে। রাজস্ব আদায়ের জন্য মহাজনদের ইজারা দেওয়া হলে তারা উচ্চহারে রাজস্ব নির্ধারণ করে। (ii) নির্মম অত্যাচার : দিকু অর্থাৎ বহিরাগত মহাজন। তারা কর আদায় করতে গিয়ে কোলদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালায় ফলে কোলেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।
৩.৭ “অস্ত্র আইন” কী?
উত্তরঃ ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিটন ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে অস্ত্র আইন জারি করেন। এর ফলে অস্ত্র রাখার ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ চালু হয়। অস্ত্র আইনে বলা হয় যে, কোনো ভারতীয় আত্মরক্ষার জন্যও অস্ত্র রাখতে পারবে না। অন্যদিকে ইউরোপীয়রা তাদের প্রয়োজনে অস্ত্র রাখতে পারবে। অর্থাৎ অস্ত্র আইন ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। লর্ড লিটন ভারতীয়দের ব্রিটিশবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য অস্ত্র আইন জারি করেন।
৩.৮ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মরণীয় কেন?
উত্তরঃ বাংলা চিত্রশিল্প ও কার্টুন শিল্পের (ব্যঙ্গচিত্র) ক্ষেত্রে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সমাজের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর অঙ্কিত 'খল ব্রাহ্মণ', 'প্রচন্ড মমতায়', 'জাঁতাসুর' প্রভৃতি ব্যঙ্গচিত্র সে সময় বাঙালিদের মধ্যে ব্যপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।
৩.৯ বসু বিজ্ঞান মন্দিরে কোন কোন বিষয়ের গবেষণা হতো?
উত্তরঃ জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁর বসু বিজ্ঞান মন্দিরে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, মাইক্রো বায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োফিজিক্স, পরিবেশ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশ্ব মানের গবেষণার ব্যবস্থা করেন।
৩.১০ কাকে “বাংলা মুদ্রণ শিল্পের জনক” বলা হয় এবং কেন?
উত্তরঃ চার্লস উইলকিন্স 1778 সালে হুগলির চুঁচুড়ায় একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাপাখানায় তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষরের টাইপ বা নকশা তৈরি করেন। এবং বাংলা ভাষায় বই প্রকাশ শুরু করেন। এই কারণে তাকে 'বাংলা মুদ্রণ শিল্পের জনক' বলা হয়।
৩.১১ লর্ড কার্জন কেন বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) করেন?
উত্তরঃ বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে কার্জন চেয়েছিলেন হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে বাঙালির সংহতিকে সমূলে বিনাশ করতে। উনিশ শতক থেকেই বাংলার মনীষীগণ নবজাতীয়তাবোধ ও নবজাগরণের যে সূচনা ঘটিয়েছিলেন তার প্রভাব পড়েছিল সারা ভারতবর্ষেই। বাংলার ঐক্যের বিনাশের প্রয়োজন প্রসঙ্গে রিজলি এক অফিসিয়াল নোটএ লিখেছিলেন – ঐক্যবদ্ধ বাংলা এক বিরাট শক্তি । বাংলা বিভক্ত হলে এই ঐক্য থাকবে না । আমাদের লক্ষ্য সংঘবদ্ধ শত্রুপক্ষকে খণ্ড করে দুর্বল করে ফেলা।
৩.১২ “সীমান্ত গান্ধী” কাকে বলা হতো এবং কেন?
উত্তরঃ খান আবদুল গফফর খানকে ‘সীমান্ত গান্ধি’ বলা হত। খান আবদুল গফফর খান ছিলেন গান্ধিবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে, মহাত্মা গান্ধির আদর্শে আন্দোলন করেছিলেন, বলে তাকে ‘সীমান্ত গান্ধি’ বলা হত। তাঁর নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে, আইন অমান্য আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছিল।
৩.১৩ বখস্ত ভূমি আন্দোলন কী?
উত্তরঃ ১৯৩০-এর মন্দার দরুন বিহারে যে জমির জনা বাকি পড়েছিল জমিদাররা সেই জমিগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে নিজেদের খাস জমি বা বখস্ত’-তে পরিণত করে এবং বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বখস্ত জমি থেকে প্রজাদের উচ্ছেদ শুরু হয়। এর প্রতিবাদে গয়া, মুঙ্গের, পাটনা, ছোটোনাগপুর-সহ বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু হয় বখস্ত আন্দোলন। সহজানন্দ সরস্বতী বিহার কিষান সভা গঠনের মাধ্যমে জমিদার বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন।
৩.১৪ অসহযোগ আন্দোলনের দুই মহিলা নেত্রীর নাম লেখো।
উত্তরঃ অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন সরোজিনী নাইডু। তিনি জাতীয়বাদী আন্দোলনের নারীদের অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রেরণা জোগান। এবং নেলি সেনগুপ্তা ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে স্টিজার ধর্মঘটে তিনি নেতৃত্ব দেন।
৩.১৫ রশিদ আলি দিবস কী?
উত্তরঃ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশদের হাতে বন্দি আজাদ হিন্দ বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি রশিদ আলির বিচার হয়। বিচারে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন তিনি। এই দণ্ডের প্রতিবাদে মুসলিম ছাত্র লিগ কলকাতায় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি দিনটি রশিদ আলি দিবস হিসেবে পালনের কথা ঘোষণা করে।
৩.১৬ দলিত কাদের বলা হয়?
উত্তরঃ হিন্দু বর্ণব্যবস্থায় জন্ম ও পেশাগত পরিচিতির বিচারে যেসব মানুষ সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থান করে এবং বিভিন্ন সময়ে উচ্চবর্ণের দ্বারা সামাজিক বঞ্ছনার শিকার হয়, তারা সাধারণভাবে দলিত নামে পরিচিত।
বিভাগ-‘ঘ’ ৪
বিভাগ-‘ঘ’ ৪। সাতটি বা আটটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্ততঃ ১ টি করে মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ৬×৪=২৪
উপবিভাগ-ঘ. ১ ৪.১ ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা কী?
উত্তরঃ ইতিহাসের তথ্যসংগ্রহে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা :
[1] তথ্যের সহজলভ্যতা : ইন্টারনেটের সহায়তায় অতি সহজে এবং ঘরে বসে ইতিহাস-সহ দুনিয়ার যাবতীয় তথ্য জেনে নেওয়া যায়। অন্য কোনো মাধ্যম থেকে এরূপ সহজে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। [2] স্বল্প অর্থব্যয় : বিভিন্ন বইপত্র কিনে, গ্রন্থাগার বা গবেষণাগারে নিয়মিত যাতায়াত করে ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে যে বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করতে হয়, তা ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে করতে হয় না। খুব সামান্য অর্থব্যয় করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেসব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। [3] সময় সাশ্রয় : বইপত্র বা অন্য কোনো সূত্র থেকে কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়। কিন্তু ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে খুব বেশি সময় ব্যয় করতে হয় না। ইন্টারনেটের মাধ্যমে নানা ধরনের অনলাইন লাইব্রেরি থেকে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ কোনো বইয়ের কপি, অনলাইন আর্কাইভ থেকে আসল রিপোর্টের কপি প্রভৃতি পাওয়া সম্ভব।
ইতিহাসের তথ্যসংগ্রহে ইনটারনেট ব্যবহারের অসুবিধা :
[1] নির্ভরযোগ্যতার অভাব: ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলি কতটা যথার্থ বা নির্ভরযোগ্য তা যাচাই করা খুব কঠিন। একই বিষয়ে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে পৃথক পৃথক তথ্য থাকায় পাঠক বা গবেষকরা বিভ্রান্ত হন। [2] মনগড়া তথ্য: ইন্টারনেটে আজকাল যে-কেউ নিজের মনগড়া ভুল তথ্য আপলোড করছে। ফলে তা গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করছে। [3] গবেষণার মান হ্রাস: ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন অসত্য বা অর্ধসত্য তথ্য ব্যবহার করতে গিয়ে পাঠক ও গবেষকগণ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং গবেষণার গুণগত মান কমে, যাচ্ছে।
উপসংহার: উক্ত আলোচনা গুলির সত্ত্বেও আজকের এই ‘তথ্য বিস্ফোরণের যুগে’ ইতিহাসের তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটেকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ইতিহাসের তথ্যসংগ্রহে সময়ের অপচয় রোধ, অফুরন্ত তথ্যের জোগান প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যাপক অবদান রয়েছে।
৪.২ “বামাবোধিনী” পত্রিকায় সমকালীন সমাজের কীরূপ প্রতিফলন ঘটেছে?
উত্তরঃ উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যেসব সাময়িকপত্রে সমকালীন বঙ্গীয় সমাজের প্রতিফলন ঘটেছে সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ নামক মাসিক পত্রিকা। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’র প্রকাশ শুরু হয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার সমাজের, বিশেষ করে নারীদের অবস্থা কেমন ছিল তা ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ থেকে জানা যায় ।
[1] নারীশিক্ষার প্রতিফলন: উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার নারীদের সামাজিক অবস্থার বিশেষ অগ্রগতি ঘটেনি। নারীশিক্ষার বিষয়টিকে সাধারণ মানুষ সুনজরে দেখত না। ফলে বাংলায় নারীশিক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটেনি। [2] নারীর মর্যাদার প্রতিফলন: এই সময় বাংলার নারীরা সাধারণত বাড়ির অন্দরমহলে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত ছিল। তাদের অধিকার ও মর্যাদা বিশেষ ছিল না। [3] সামাজিক কুসংস্কারের প্রভাব: ‘বামাবোধিনী' পত্রিকা উনিশ শতকে বাংলার বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার তুলে ধরে এসবের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা চালায়। নারীদের বাল্যবিবাহ, পুরুষদের বহুবিবাহ, মদ্যপান প্রভৃতির বিরুদ্ধে এই পত্রিকায় নিয়মিত প্রচার চালানো হয়।
উপসংহার: বাংলার তৎকালীন সামাজিক সমস্যাগুলি দূর করার উদ্দেশ্যে ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ নিয়মিত প্রচার চালায়। পত্রিকাটি নারীশিক্ষার প্রসার, নারীর সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাংলায় নারী আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
উপবিভাগ-ঘ.২ ৪.৩ বিপ্লব, বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো।
উত্তরঃ ইতিহাসের আলোচনায় আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ধারা হল ‘বিদ্রোহ’, ‘অভ্যুত্থান’ ও ‘বিপ্লব’। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে শোষক ও অত্যাচারী প্রভুদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠী প্রতিবাদে শামিল হয়েছে। এই প্রতিবাদ বা ক্ষোভের প্রকাশ বিভিন্ন ‘বিদ্রোহ’ বা ‘অভ্যুত্থান’ বা ‘বিপ্লব’-এর মাধ্যমে হতে পারে। ‘বিদ্রোহ’, ‘অভ্যুত্থান’ও ‘বিপ্লব’-এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। যেমন-
১. বিপ্লব : ‘বিপ্লব’ কী? ‘বিপ্লব’ বলতে বোঝায় প্রচলিত ব্যবস্থার দ্রুত, ব্যাপক ও আমূল পরিবর্তন। ‘বিপ্লব’ হল ‘বিদ্রোহ' এবং ‘অভ্যুত্থান’-এর চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক।
উদাহরণ : [a] অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের দ্বারা ইউরোপের শিল্পব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। [b] ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের দ্বারা ফ্রান্সের পূর্বতন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্রুত ও আমূল পরিবর্তন ঘটে। বিদ্রোহকে আবার বিপ্লবের প্রাথমিক ধাপ বলা যায় ৷
২. বিদ্রোহ : বিদ্রোহ কী? বিদ্রোহ বলতে বোঝায় কোনো প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তনের দাবিতে বিরোধী জনসমষ্টির আন্দোলন। বিদ্রোহ স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে। বিদ্রোহ সফল হলে পূর্বতন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে, ব্যর্থ হলেও বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন সম্ভব।
উদাহরণ : ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে রংপুর বিদ্রোহ, পাবনা বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ্ প্রভৃতি কৃষকবিদ্রোহ এবং সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭ খ্রি.) প্রভৃতি হল বিদ্রোহের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। বিদ্রোহের গতি অনেক সময় থেমে যায়। যেমন, রংপুর বিদ্রোহের মতো ঘটনায় আগে প্রচলিত ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আবার নীল বিদ্রোহের পর সরকার নীল কমিশন নিয়োগ করে নীলচাষিদের ওপর অত্যাচার লাঘবের ব্যবস্থা করে।
৩. অভ্যুত্থান : অভ্যুত্থান কী?: অভ্যুত্থান বলতে বোঝায় কোনো প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজ গোষ্ঠীর একাংশের সংগ্রাম। অভ্যুত্থান দীর্ঘমেয়াদী হয় না। অভ্যুত্থান সাধারণত খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়। অভ্যুত্থানে বিরোধী গোষ্ঠীর ভূমিকা থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে। তবে নিজ গোষ্ঠীর একাংশের স্বার্থসিদ্ধির বিষয়টি ‘অভ্যুত্থান’-এ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
উদাহরণ : [a] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের · ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একাংশ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সিপাহি বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহ সংঘটিত করে। [b] ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নৌসেনাদের নৌবিদ্রোহ সম্পন্ন হয়। [c] স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেনাপতি মহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করে। এগুলি অভ্যুত্থান হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তবে এগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।
৪.৪ মহাবিদ্রোহের সময় কোম্পানীর ভারতীয় সিপাহীদের অসন্তোষের কী কী কারণ ছিল?
উত্তরঃ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । এই মহাবিদ্রোহ ভারতে ব্রিটিশ শাসন কে প্রায় ভাসিয়ে দিতে বসেছিল। এই বিদ্রোহ কোম্পানির ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে সূত্রপাত হলেও অল্পদিনের মধ্যে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পরিব্যপ্ত হয়। প্রায় এক বছর ধরে লক্ষ লক্ষ কৃষক , শ্রমিক এবং সিপাহীরা সাহসের সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল।
- ইংরেজদের অসভ্য আচরণ : ইংরেজ কর্মচারীরা ভারতীয় সিপাহিদের ঘৃণা করত। তারা ভারতীয় সিপাহিদের নেটিভ, নিগার, শুয়োর প্রভৃতি বলে গালাগালি করত।
- ভারতীয় সৈন্যদের অবহেলা : ভারতীয় সিপাহিদের বেতন, পদমর্যাদা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা ব্রিটিশ সৈন্যদের তুলনায় কম ছিল। ভারতীয়দের পদোন্নতির সুযোগ ছিল না ও বাসস্থান ছিল নিম্নমানের। ঐতিহাসিক হোস উল্লেখ করেছেন, “একজন সিপাহি হায়দার আলির মতো নিপুণ ও দক্ষ হলেও সে একজন অত্যন্ত সাধারণ ইংরেজ সৈন্যের মতো মর্যাদাও আশা করতে পারত না।” একজন ইংরেজ সৈন্যের মাসিক বেতন ছিল ৯০ ডলার ও একজন ভারতীয় সৈন্যের মাসিক বেতন ছিল ৭ টাকা।
- ধর্মীয় অসন্তোষ : ইংরেজ সামরিক কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সিপাহিদের তিলক কাটা, দাঁড়ি ও টিকি রাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল বলে তারা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ‘জেনারেল সার্ভিস এনলিস্টমেন্ট অ্যাক্ট’ পাস করে ভারতীয় সিপাহিদের যে-কোনো জায়গায় যাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। কালাপানি বা সমুদ্রযাত্রা হিন্দু সিপাহিদের নিষিদ্ধ হলেও তা ইংরেজরা অগ্রাহ্য করে।
- সিপাহিদের পরিবারের উপর অত্যাচার : ভারতীয় সিপাহিরা ছিল সাধারণত কৃষক পরিবারের সন্তান। ভারতীয় কৃষকরা বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে ইংরেজদের প্রতি ক্ষুব্ধ হলে সিপাহিদের পরিবারে প্রতি ইংরেজদের ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল।
- ভাতা : যুদ্ধের জন্য সিপাহিদের দূরদেশে যেতে হত। এসময় ইংরেজ সৈন্যদের বেতন ছাড়াও অতিরিক্ত টাকা বা ভাতা (allowance) দেওয়া হত। কিন্তু ভারতীয় সিপাহিদের কেবল বেতন দেওয়া হত, কোনো ভাতা দেওয়া হত না। এজন্য ভারতীয় সিপাহিরা বিক্ষুব্ধ হয়।
- এনফিল্ড রাইফেল : ভারতীয় সেনাবাহিনীতে এই অস্ত্র প্রবর্তন করা হয়। এর কার্তুজ বা টোটা দাঁতে কেটে রাইফেলে ভরতে হত। কার্তুজের গায়ে যে প্রলেপ থাকত, গুজব রটে তা গোরু ও শূকরের চর্বি দিয়ে তৈরি। হিন্দু ও মুসলিম সিপাহিরা ধর্ম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় ওই কার্তুজ ব্যবহারে অসম্মত হয় পরিণামে সিপাহি বিদ্রোহ ঘটে।
উপবিভাগ-ঘ.৩ ৪.৫ কারিগরি শিক্ষার বিকাশে বাংলায় টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের কী ভূমিকা ছিল?
উত্তরঃ ব্রিটিশ সরকার ভারতে পাশ্চাত্য ধাঁচের বিভিন্ন অফিস আদালত প্রতিষ্ঠা করলে এসব স্থানে কাজের জন্য আধুনিক পাশ্চাত্য ও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মচারীর প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনে সরকার ভারতে পাশ্চাত্য ধাঁচের আধুনিক শিক্ষার সূচনা করে। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা হয় বাংলায়। এই সময় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স, কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ, বসু বিজ্ঞান মন্দির, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, বেঙ্গল টেকনিকাল ইন্সটিটিউট প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বাংলা তথা ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি
শিক্ষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
বেঙ্গল টেকনিকাল ইন্সটিটিউট :
[i] প্রতিষ্ঠা: তারকনাথ পালিতের প্রচেষ্টায় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে (২৫ জুলাই) কলকাতায় বেঙ্গল টেকনিকাল ইন্সটিটিউট নামে একটি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল টেকনিকাল ইন্সটিটিউট-এর সঙ্গে মিলে যায় ৷ [ii] বিষয়-বৈচিত্র্য: কলাবিভাগের পাশাপাশি এখানে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রযুক্তি, শিল্পপ্রযুক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণা কর্ম প্রকাশের জন্য এই প্রতিষ্ঠান থেকে ‘টেক’ নামে একটি জার্নাল প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়।
৪.৬ টীকা লেখো: মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা।
উত্তরঃ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পর ভারতে দ্রুতগতিতে কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রসার ঘটতে থাকে।
[1] কমিউনিস্টদের প্রসার: ১৯২০-এর দশকের শুরু থেকে ভারতের কমিউনিস্টরা দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক যোগ দেয় এবং পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। [2] সরকারের উদবেগ : কমিউনিস্ট ভাবধারা ও কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের দ্রুত প্রসারে সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টদের দমন ও শ্রমিক আন্দোলন থামিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকার মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় বিভিন্ন কমিউনিস্ট নেতাকে জড়িয়ে দেয়। [3] মামলার রায়: ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার রায় প্রকাশিত হয়। মামলায় ৩৩ জন কমিউনিস্ট নেতাকে অভিযুক্ত করা হয়। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মুজাফফর আহমেদ, শিবনাথ ব্যানার্জি, ধরণী গোস্বামী, এস এ ডাঙ্গে, পি সি জোশী, ফিলিপ স্প্ল্যাট, গঙ্গাধর অধিকারী প্রমুখ। মামলার রায়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্টদের যাবতীয় প্রচারকার্য নিষিদ্ধ হয়।
উপসংহার: ব্রিটিশ সরকার ভারতে বামপন্থী আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ‘মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা’ শুরু করে। এই মামলার রায়ে ৩৩ জন গুরুত্বপূর্ণ কমিউনিস্ট নেতার কারাদণ্ড হলে ভারতে বামপন্থী আন্দোলন সংকটের মুখে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যে সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে বামপন্থী আন্দোলন আপাতত স্তিমিত হয়ে পড়ে।
উপবিভাগ-ঘ.৪ ৪.৭ ভগৎ সিং কেন স্মরণীয়?
উত্তরঃ বিপ্লবী ভগৎ সিং নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে আত্মত্যাগের যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তা দেশবাসীকে মুগ্ধ করে। [1] বিপ্লবের সূচনা : ভগৎ সিং কৈশোরেই বিপ্লবী ভাবধারায় আকৃষ্ট হন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি গান্ধিজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে সরকারি স্কুল-বই ও বিলিতি পোশাক পুড়িয়ে ফেলেন।
[2] নেতৃত্বের সূচনা: ভগৎ সিং হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন’-এর সদস্য হওয়ার পরপরই এই দলের নেতৃত্ব দেন। পরে এই সংগঠনের ব্যাপক পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় ‘হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন’। ভগৎ সিং ‘নওজওয়ান ভারত সভা’, ‘কীৰ্তি কিষান পাৰ্টি’ প্রভৃতি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে বিপ্লবীদের সংঘবদ্ধ করতে থাকেন। [3] সন্ডার্সকে হত্যা: সাইমন কমিশন-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুলিশের লাঠির আঘাতে লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে ভগৎ সিং, রাজগুরু ও আজাদ পুলিশ অফিসার সন্ডার্সকে হত্যা করেন। [4] আইনসভায় বোমা: ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ভগৎ সিংও বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লি আইনসভায় বোমা নিক্ষেপ করেন। এরপর তাঁরা ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’, ‘সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক’, ‘দুনিয়ার মজদুর এক হও’ জাতীয় নানা স্লোগান দিতে দিতে পুলিশের হাতে ধরা দেন। জেলে থাকার সময় ব্রিটিশ ও ভারতীয় বন্দিদের মধ্যে সমানাধিকারের দাবিতে ভগৎ সিং টানা ৬৪ দিন অনশন চালান।
উপসংহার: লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার (১৯২৯ খ্রি.) রায়-এ ভগৎ সিং-সহ রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসি হয়। ফাঁসির আগে ভগৎ সিংকে জানানো হয়, আর মাত্র আড়াই ঘণ্টা বাকি। ভগৎ সিং বললেন, “আড়াই ঘণ্টা কেন ! এখনই নিয়ে চলো! আমরা তো প্রস্তুত হয়েই আছি।”
৪.৮ জুনাগড় রাজ্যটি কীভাবে ভারতভুক্ত হয়?
উত্তরঃ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ভারতীয় ভূখণ্ডের অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য ভারতে যোগদান করলেও কয়েকটি রাজ্য ভারতে যোগ দিতে অস্বীকার করে। এগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল কাথিয়াবাড় উপদ্বীপে অবস্থিত জুনাগড়। [1] সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি : দেশীয় রাজ্য জুনাগড়ের জনসংখ্যার অন্তত ৮০ শতাংশই ছিল হিন্দু। কিন্তু সেখানকার মুসলিম নবাব জুনাগড়কে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। জুনাগড়ের দেওয়ান শাহনওয়াজ ভুট্টো-ও ছিলেন মুসলিম লিগের উগ্র সমর্থক। [2] প্ৰজাবিদ্রোহ : জুনাগড়ের নবাব রাজ্যটিকে পাকিস্তানের সঙ্গে
যুক্ত করতে চাইলে সেখানকার অ-মুসলিম প্রজাদের মধ্যে প্রবল গণবিক্ষোভ ও ব্যাপক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।
[3] সেনা অভিযান : জুনাগড়ে তীব্র প্রজাবিদ্রোহের ফলে সেখানকার নবাব পাকিস্তানে পালিয়ে যান। এই পরিস্থিতিতে ভারতের সেনাবাহিনী জুনাগড়ে প্রবেশ করে। [4] গণভোট: জুনাগড়ের বাসিন্দারা ভারত, না পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে আগ্রহী তা জানার জন্য সেখানে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গণভোট নেওয়া হয়। গণভোটে সেখানকার মানুষ ভারতে যোগদানের পক্ষে মত দেয়। [5] ভারতে যোগদান: গণভোটের পর জুনাগড় ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে (জানুয়ারি) ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়।
উপসংহার: জুনাগড়ের ভারতে অন্তর্ভুক্তির ফলে দেশীয় রাজ্য দখলে এনে পাকিস্তানের শক্তিবৃদ্ধির প্রয়াস ধাক্কা খায়। এতে ভারতের সুবিধা হয়।
বিভাগ-‘ঙ’ ৫
বিভাগ-‘ঙ’ ৫। পনেরো বা ষোলটি বাক্যে যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দাও: ১×৮=৮
৫.১ বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। বিদ্যাসাগর কতটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন?
উত্তরঃ ঊনবিংশ শতকের একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও সমাজসংস্কারক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১ খ্রি.)। মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগরের প্রতি সন্মান জানিয়ে লিখেছিলেন—“বিধাতা বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্গভূমিকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।”
বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বিদ্যাসাগরের অবদান : পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীর অকাল বৈধব্য জীবনের দুঃখদুর্দশা দেখে বিচলিত হয়ে বিধবাবিবাহ প্রথা প্রবর্তনের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত তা প্রমাণ করার জন্য তিনি ‘পরাশর সংহিতা’-র শ্লোক উদ্ধৃত করে লিখেছিলেন, “স্বামী নিরুদ্দেশ হলে, মারা গেলে, ক্লীব হলে, সংসারধর্ম ত্যাগ করলে অথবা পতিত হলে স্ত্রীর পুনর্বিবাহ শাস্ত্রসম্মত।” তাঁর এই উদ্যোগের বিরোধিতা করে রক্ষণশীল সমাজপতিরা নানাভাবে বিদ্যাসাগরকে লাঞ্ছিত করলেও তিনি এই আন্দোলন চালিয়ে যান। বিদ্যাসাগরের আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই লর্ড ডালহৌসী বিধবাবিবাহ আইন পাস করেন।
তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে বর্ধমান জেলার পলাশডাঙার ব্রহ্মানন্দ মুখার্জীর দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতীদেবীর বিবাহ দেন (১৮৫৬ খ্রি., ৭ ডিসেম্বর)। এরপরে তিনি পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে ভবসুন্দরী নামে ১৮ বছরের এক বিধবার বিবাহ দেন। ১৮৫৬-১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিদ্যাসাগর নিজে ৮২ হাজার টাকা খরচ করে মোট ৬০টি বিধবাবিবাহের আয়োজন করেন। দরিদ্র বিধবাদের আর্থিক সাহায্যের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফান্ড (১৮৭২ খ্রি.)। শেষপর্যন্ত ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই (XV রেগুলেশন দ্বারা) বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়।
স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, রামকৃষ্ণদেবের পর আমি বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করি (“After Ramakrishna, I follow Vidyasagar”) ন্যায় ও সত্যের প্রতি তিনি যতটা অনুগত ছিলেন, ঠিক ততটাই প্রতিবাদী ছিলেন অন্যায় ও অসত্যের (extremist) কোনটাই বিদ্যাসাগর ছিলেন না। সমকালীন সমাজে তিনি ছিলেন সত্যকার বাস্তববাদী (realist)। আদর্শবাদের সঙ্গে বাস্তববাদের যে সমন্বয় তাঁর চরিত্রে ঘটেছিল, তেমনি আর কারো চরিত্রে ঘটেনি।”
৫.২ সিপাহী বিদ্রোহকে কী একটি জাতীয় বিদ্রোহ বলা যায়? সপক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা করো।
উত্তরঃ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি বা চরিত্র নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক ও মতবৈষম্য রয়েছে। একপক্ষের মতে, এটি ‘সিপাহি বিদ্রোহ’। অপরপক্ষ বলেন, এটি সমগ্র ভারতবাসীর আন্দোলন বা ‘জাতীয় আন্দোলন’। তা ছাড়াও অনেকে এই বিদ্রোহকে ‘ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম’, ‘কৃষক বিদ্রোহ’, ‘সামন্ততান্ত্রিক প্রতিবাদ’ ইত্যাদি বলেছেন।
১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলা যায় কি না তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে —
- পক্ষে যুক্তি: জাতীয়তাবাদী নেতা বিনায়ক দামোদর সাভারকর, পি. সি. জোশি প্রমুখ এই বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। (i) দেশপ্রেমিক বীর সাভারকর লিখেছেন—“১৮৫৭-র বিদ্রোহ ছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ।” (ii) পি.সি. জোশি তাঁর ‘1857 in Our History' প্রবন্ধে লিখেছেন—“মহাবিদ্রোহ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ।” (ii) অধ্যাপক সুশোভন সরকারের মতে—“সিপাহি বিদ্রোহকে জাতীয় সংগ্রাম না বললে ইতালির কার্বোনারী আন্দোলনকে ইতালির মুক্তিযুদ্ধ বলা যাবে না।”
- বিপক্ষে যুক্তি: ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ প্রমুখ বিদগ্ধ পণ্ডিত সিপাহি বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলার পক্ষপাতী নন। (i) সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর ‘Eighteen Fifty-Seven’ গ্রন্থে লিখেছেন, “১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা চলে না।” (ii) ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের তথাকথিত প্রথম জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ, না ছিল প্রথম, না ছিল জাতীয়, না ছিল স্বাধীনতার যুদ্ধ। তাঁর মতে এই আন্দোলনে ভারতের সাধারণ মানুষ যোগ দেয়নি। (iii) ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ বলেছেন, “এই বিদ্রোহে যতজন সৈন্য যোগ দিয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি সৈন্য বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল।” পরিশেষে, সবদিক বিচার করে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলা যায় না। এই মহাবিদ্ৰোহ মূলত ছিল ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রথম বৃহত্তম অভ্যুত্থান।
৫.৩ ভারত ছাড়ো আন্দোলনে শ্রমিকদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি সম্বন্ধে একটি টীকা লেখো।
উত্তরঃ গান্ধিজির নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ৮ আগস্ট বোম্বাই অধিবেশনে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তাব করে। প্রস্তাবের পরের দিনই সরকার কংগ্রেসের প্রথম সারির প্রায় সকল নেতাকে গ্রেফতার করলে জনগণ নিজের হাতে আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব তুলে নেয়। এই আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণির অংশগ্রহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
[1] ব্রিটিশ বিরোধিতা: ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে শ্রমিকরা প্রাথমিক পর্বে ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের দাবি জানায়। তাদের বিশ্বাস ছিল ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগ করলে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে। [2] শ্রমিকদের দাবি: ভারত ছাড়ো আন্দোলনে শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ে আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠে। শ্রমিকদের দাবিদাওয়াগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল তাদের কাজের সময়কাল কমানো, বেতন বৃদ্ধি, বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার সুযোগ, বিমার বন্দোবস্ত, ভাতার প্রচলন, সন্তানদের জন্য শিক্ষার সুযোগ প্রভৃতি। [3] ধর্মঘট পালন: ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কমিউনিস্ট দল উৎপাদন প্রক্রিয়া বন্ধ না করার আহ্বান জানায়। কিন্তু শ্রমিকরা কলকারখানার উৎপাদন বন্ধ করে দেয় এবং স্থানে স্থানে ধর্মঘট ও হরতাল পালন করে। কমিউনিস্ট নেতারা ভারত ছাড়ো আন্দোলন থেকে দূরে থাকলেও বহু শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেয়। [4] শ্রমিক আন্দোলনের প্রসার: ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় ভারতের সর্বত্র শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বাংলা, বিহার, দিল্লি, বোম্বাই, লখনউ, মাদ্রাজ, কানপুর, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে শ্রমিক আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। [5] খণ্ডযুদ্ধ: শ্রমিকদের ধর্মঘট ও আন্দোলনকে স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে সরকার পুলিশ ও সেনাদলের দ্বারা আন্দোলনকারীদের ওপর তীব্র দমনপীড়ন শুরু করে। ফলে সেনা ও পুলিশের সাথে শ্রমিকদের সংঘাত বাধে। বোম্বাইয়ের রাজপথে সেনা ও পুলিশের সাথে শ্রমিকদের খণ্ডযুদ্ধে প্রায় ২৫০ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। এভাবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
Workers and Peasants Party :
ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে ‘ওয়ার্কস অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি’ শ্রমিক ও কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ভারতে ব্যাপক হারে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। এবং সরাসরিভাবে কাজ করার ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির নানা অসুবিধা থাকায়তারা শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থে ১৯২৫ খ্রিঃ ১ নভেম্বর ‘দি লেবার স্বরাজ পার্টি অব দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' নামে কলকাতায় একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয় পরে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ওয়ার্কস অ্যান্ড পেজেন্টস পাটি "Workers and Peasants Party"।
ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস্ পার্টির উদ্দেশ্যগুলি হল— (১) শ্রমিকদের কাজের সময়সীমা নির্ধারণ (২) বাকস্বাধীনতা অর্জন, (৩) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অর্জন, (৪) জমিদারি প্রথার বিলোপসাধন এবং (৫) সর্বনিম্ন মজুরি আইন
প্রবর্তন ইত্যাদি। এই সংগঠনটি তার উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে যে আন্দোলনগুলি চালিয়েছিল, জাতীয় কংগ্রেসও সেইসব আন্দোলনের প্রতি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সহানুভূতি দেখিয়েছিল।
উপসংহার : কলকাতার ধাঁচে পরবর্তীকালে পাঞ্জাব ও বোম্বাই সমেত আরও অন্যান্য অঞ্চলে এইরূপ সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। তবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সংগঠনটি সাফল্য পেলেও কৃষকদের সংগঠিত করা ক্ষেত্রে সাফল্য ছিল খুব সামান্য। তবে আন্দোলনের ব্যাপকতায় বিচলিত সরকার একটি তদন্ত কমিশন বসালে সেই কমিশন খাজনা বৃদ্ধিকে ৬.০৩ শতাংশ বৃদ্ধি করে। অবশেষে কৃষকরাও খাজনা দিতে সম্মত হলে বারদৌলি সত্যাগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটে।