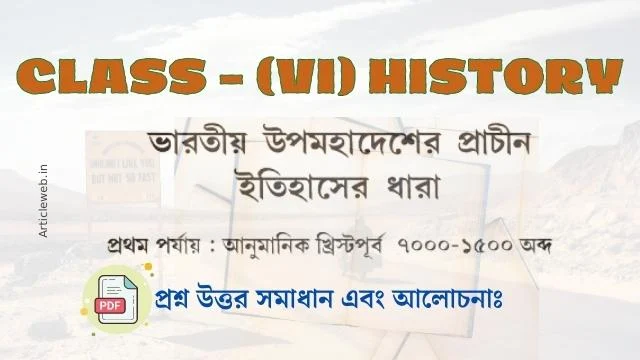ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা : অতীত-ঐতিহ্য ইতিহাস পৃষ্ঠা নং-৪৩ প্রশ্ন উত্তর তৃতীয় অধ্যায়
১. বেমানান শব্দটি খুঁজে বের করাে :
১.১) তামা, কাঁসা , পাথর, লােহা।
উত্তর : কাঁসা
১.২) ঘােড়া, হাতি, গন্ডার, ষাঁড়।
উত্তর : গন্ডার
১.৩) কালিবঙ্গান , মেহেরগড়, বানাওয়ালি, ঢােলাবিরা।
উত্তর : মেহেরগড়
২. নীচের বাক্যগুলির কোনটি ঠিক কোটি ভুল লেখাে :
২.১) লিপির ব্যবহার সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য।
উত্তর : ঠিক
২.২) মেহেরগড় সভ্যতা আবিষ্কার করেন দয়ারাম সাহানি।
উত্তর : ভুল
২.৩) হরপ্পা সভ্যতা প্ৰাক-ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতা।
উত্তর : ঠিক
২.৪) হরপ্পার মানুষ লিখতে জানতেন।
উত্তর : ঠিক
৩. সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করাে :
৩.১) হরপ্পা সভ্যতার বাড়িঘরগুলি তৈরি হত—(পাথর দিয়ে/ পােড়া ইট দিয়ে/কাঠ দিয়ে)।
উত্তর : পােড়া ইট দিয়ে।
৩.২ হরপ্পা সভ্যতা ছিল—(পাথরের যুগের/ লােহার যুগের/তামা ও ব্রোঞ্জ যুগের) সভ্যতা।
উত্তর : তামা ও ব্রোঞ্জ যুগের।
৩.৩ ভারতীয় উপমহাদেশে হরপ্পাতেই—(প্রথম নগর/প্রথম গ্রাম/দ্বিতীয় নগর) দেখা গিয়েছিল।
উত্তর : প্রথম নগর।
ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা বড় প্রশ্ন উত্তর
৪. নিজের ভাষায় ভেবে লেখাে : (তিন/চার লাইন)৪.১) তােমার জানা কোনাে একটি শহরের সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার মিল-অমিলগুলি খুঁজে বার করাে।
উত্তরঃ আমার শহর কলকাতার সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার কিছু মিল আছে। হরপ্পার মতাে কলকাতার নর্মদা ব্যবস্থা অনেক উন্নত। ডাস্টবিন ব্যবস্থা আছে। হরপ্পাতে যেমন সমাজে শ্রেণিবৈষম্য ছিল অর্থাৎ ধনী ও গরিবদের বাসস্থান ও জীবনযাপন আলাদা ছিল। সেরকম কলকাতায় গরিবরা বস্তি নামক স্থানে বসবাস করে। এমন তাদের জীবনমাত্রার মান অনেক অনুন্নত। হরপ্পা নগরে শস্যাগার ও স্নানাগার পাওয় গেছে যা কলকাতা শহরে নেই। বেশির ভাগ বাড়িতে শস্যাগার সঞ্চিত রাখার স্থান ছিল বা ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কলকাতার বাড়িতে সেরকম শস্যাগারের কোনাে উল্লেখ নেই।
৪.২) সিন্ধুনদীর তীরে হরপ্পা সভ্যতার শহরগুলি কেন গড়ে উঠেছিল বলে তােমার মনে হয়?
উত্তরঃ দেখা গেছে সব বড়াে সভ্যতাই নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। হরপ্পা সিন্ধু নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল কারণ। তখন জলপথে যােগাযােগ ব্যবস্থা উন্নত ছিল। কম সময়ে ও কম খরচে বাণিজ্যের সুবিধা ছিল জলপথে। তাই নদী অর্থনৈতিক ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা প্রথম পর্যায় উন্নতিতে সাহায্য করেছিল। এছাড়াও কৃষিকাজ নদীর তীরবর্তী স্থানে হত। উর্বর পলিমাটি থাকায় কৃষিকাজেরও উন্নতি হয়। কৃষিকাজের উন্নতির সঙ্গে পশুপালন সম্পর্কযুক্ত তাই সিন্ধুনদীর তীরে হরপ্পা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।
৪.৩) হরপ্পা সভ্যতায় কী ধরনের বাড়িঘর পাওয়া গেছে? সেগুলিতে কারা থাকত বলে মনে হয়?
উত্তরঃ পােড়া ইটের তৈরি বাড়ির নিদর্শন হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া যায়। তাছাড়া ইমারত অর্থাৎ বড়াে বাড়ি যেমন ছিল তেমনি পাশাপাশি ছােটো বাড়ির নিদর্শনও পাওয়া যায়। বাড়িতে শস্য রাখার তাকও ছিল। সুতরাং বলা যায় বাড়িতে শস্য জমায়েত রাখার ব্যবস্থা ছিল। আর তখনকার সময় গরিব ও ধনী লােকের ভেদাভেদ ছিল তা জানা যায়। ধনী লােকেরা বড়াে বাড়িতে থাকত এবং গরিব লােকেরা ছােটো বাড়িতে থাকত এবং যৌথ পরিবার ছিল।
৪.৪) তােমার কি মনে হয়, হরপ্পা সভ্যতার মানুষ স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন? তােমার স্থানীয় অঞ্চলে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হরপ্পার মানুষের থেকে কোন কোন বিষয় তুমি শিখবে?
উত্তরঃ হ্যাঁ, হরপ্পা সভ্যতার মানুষরা স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কারণ তারা শৌচাগার ও বাঁধানাে পরিষ্কার স্নানাগার ব্যবহার করত। ঘরের সাথে ছােটো ছােটো নর্দমা ছিল যা বড়াে নর্দমার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পাকা নদর্মা দিয়ে জল নিকাশি ব্যবস্থাও ছিল। বড়াে নর্দমাগুলি ঢাকা থাকত। নগরগুলি পরিষ্কার ছিল। আমার স্থানীয় অঞ্চলে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হরপ্পা থেকে আমি ওদের জল নিকাশি ব্যবস্থা শিখব, যা আমাদের পরিবেশকে পরিষ্কার রাখব। আমাদের জায়গাটিকে পরিষ্কার রাখব এবং আবর্জনামুক্ত রাখব। এইসব ব্যবস্থা শিখব হরপ্পা সভ্যতা থেকে।
❐ হাতে কলমে করো : ৫.১) এবং ৫.২) নিজে করো ?
◈ আরো পড়ুনঃ ◈
❏ প্র্যাকটিস সেট প্রশ্নও উত্তর ☟☟☟
১. কাদের ঘিরে মানুষের জীবনযাত্রা গড়ে ওঠে?
উত্তরঃ বসতবাড়ি, কৃষিকাজ এবং পশুপালন।
২. আদিম গােষ্ঠী সমাজে মানুষ কীভাবে জোট বাঁধত?
উত্তরঃ আদিম গােষ্ঠী সমাজে মানুষ সুযােগ-সুবিধা অনুযায়ী জোট বাঁধত।
৩. মেহেরগড় সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল?
উত্তরঃ পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে বােলান গিরিপথ থেকে খানিক দূরে।
৪. মেহেরগড় সভ্যতাকে কটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে?
উত্তরঃ তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। ৭০০০-৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ প্রথম পর্যায়। ৫০০০-৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ দ্বিতীয় পর্যায় এবং ৪৩০০-৩৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ– তৃতীয় পর্যায়।
৫. হরপ্পা সভ্যতা কোন যুগের সভ্যতা?
উত্তরঃ তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা।
৬. হরপ্পা নগরীর ধ্বংসাবশেষ কে আবিষ্কার করেন?
উত্তরঃ প্রত্নবিজ্ঞানী দয়ারাম সাহানি।
৭. মহেঞ্জোদাড়াে ধ্বংসাবশেষ কে আবিষ্কার করেন?
উত্তরঃ প্রত্নবিজ্ঞানী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৮. কত খ্রিস্টাব্দে মহেঞ্জোদাড়াে ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা হয়?
উত্তরঃ ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে হরপ্পা ও ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মহেঞ্জোদাড়াে ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা হয়।
৯. হরপ্পা সভ্যতার কবে সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে বলে অনুমান করা হয়?
উত্তরঃ খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত।
১০. কতটা জায়গা জুড়ে হরপ্পা সভ্যতা অবস্থান ছিল?
উত্তরঃ প্রায় সাত লক্ষ বর্গ কিলােমিটার জুড়ে ছড়িয়ে ছিল হরপ্পা সভ্যতা।
১১. সিটাডেল কাকে বলে?
উত্তরঃ হরপ্পার নগরগুলিতে একটি উঁচু এলাকা থাকত সেখানে ধনী লােকেরা থাকত সেই স্থানটিকে সিটাডেল বলে।
উত্তরঃ প্রত্নবিজ্ঞানী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৮. কত খ্রিস্টাব্দে মহেঞ্জোদাড়াে ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা হয়?
উত্তরঃ ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে হরপ্পা ও ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মহেঞ্জোদাড়াে ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা হয়।
৯. হরপ্পা সভ্যতার কবে সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে বলে অনুমান করা হয়?
উত্তরঃ খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত।
১০. কতটা জায়গা জুড়ে হরপ্পা সভ্যতা অবস্থান ছিল?
উত্তরঃ প্রায় সাত লক্ষ বর্গ কিলােমিটার জুড়ে ছড়িয়ে ছিল হরপ্পা সভ্যতা।
১১. সিটাডেল কাকে বলে?
উত্তরঃ হরপ্পার নগরগুলিতে একটি উঁচু এলাকা থাকত সেখানে ধনী লােকেরা থাকত সেই স্থানটিকে সিটাডেল বলে।
১২. হরপ্পাবাসীর প্রধান খাদ্য কী ছিল?
উত্তরঃ গম, যব, জোয়ার, ছােলা, মটর ও তিল।
১৩. কোন স্থান থেকে কাঠের লাঙলের ফলার দাগ পাওয়া যায়?
উত্তরঃ রাজস্থানের কালিবঙ্গান থেকে।
১৪. হরপ্পা সভ্যতায় কীসের পুজোর চল ছিল?
উত্তরঃ হরপ্পা সভ্যতায় মাতৃপুজো, পশুপতি শিবের পুজো, বৃক্ষপুজো ও ষাঁড়ের পুজোর চল ছিল।
১৫. হরপ্পা সভ্যতায় মানুষজন কোন ধাতুর ব্যবহার জানত না?
উত্তরঃ লােহা।
১৬. হরপ্পা সভ্যতার প্রধান জীবিকা কী ছিল?
উত্তরঃ : চাষবাদ।
১৭. হরপ্পাবাসীরা কীসের তৈরি অলংকার ব্যবহার করত?
উত্তরঃ সােনা, রুপাে, তামা ও হাতির দাঁতের গয়না পরত।
১৮. হরপ্পা সভ্যতা কত ধরনের ইটের ব্যবহার দেখা যায় ?
উত্তরঃ হরপ্পা সভ্যতায় দুধরনের ইটের ব্যবহার দেখা যায় (i) কাদামাটির ইট (ii) চুল্লিতে পােড়া ইট।
১৯. হরপ্পা কোন কোন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করত?
উত্তরঃ মেসােপটেমিয়া, ইরান ও তুর্কমেনিস্থান।
২০. হরপ্পা সভ্যতায় বিদেশ থেকে কী কী আমদানি করা হত?
উত্তরঃ গম, যব, জোয়ার, ছােলা, মটর ও তিল।
১৩. কোন স্থান থেকে কাঠের লাঙলের ফলার দাগ পাওয়া যায়?
উত্তরঃ রাজস্থানের কালিবঙ্গান থেকে।
১৪. হরপ্পা সভ্যতায় কীসের পুজোর চল ছিল?
উত্তরঃ হরপ্পা সভ্যতায় মাতৃপুজো, পশুপতি শিবের পুজো, বৃক্ষপুজো ও ষাঁড়ের পুজোর চল ছিল।
১৫. হরপ্পা সভ্যতায় মানুষজন কোন ধাতুর ব্যবহার জানত না?
উত্তরঃ লােহা।
১৬. হরপ্পা সভ্যতার প্রধান জীবিকা কী ছিল?
উত্তরঃ : চাষবাদ।
১৭. হরপ্পাবাসীরা কীসের তৈরি অলংকার ব্যবহার করত?
উত্তরঃ সােনা, রুপাে, তামা ও হাতির দাঁতের গয়না পরত।
১৮. হরপ্পা সভ্যতা কত ধরনের ইটের ব্যবহার দেখা যায় ?
উত্তরঃ হরপ্পা সভ্যতায় দুধরনের ইটের ব্যবহার দেখা যায় (i) কাদামাটির ইট (ii) চুল্লিতে পােড়া ইট।
১৯. হরপ্পা কোন কোন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করত?
উত্তরঃ মেসােপটেমিয়া, ইরান ও তুর্কমেনিস্থান।
২০. হরপ্পা সভ্যতায় বিদেশ থেকে কী কী আমদানি করা হত?
উত্তরঃ সােনা, রুপাে, তামা, দামি পাথর, হাতির দাঁতের তৈরি চিরুনি, পাখির
মূর্তি।
২১. হরপ্পা সভ্যতায় কী কী রপ্তানি করা হত?
উত্তরঃ বার্লি, ময়দা, তেল ও পশমজাত দ্রব্য।
২২. হরপ্পা সভ্যতায় জলপথে যােগাযােগের মাধ্যম কী ছিল?
উত্তরঃ বলদ, গাধা ও উট।
২৩. হরপ্পা সভ্যতায় সমাধি কোথায় পাওয়া গেছে?
উত্তরঃ কালিবঙ্গানে।
২৪. সিলমােহর তৈরির জন্য সিন্ধু সভ্যতার লােকেরা সাধারণত কোন ধরনের পাথর ব্যবহার করত?
উত্তরঃ স্টিটাইট নামে এক ধরনের পাথর।
২৫. লােথাল বন্দর কোথায় অবস্থিত?
উত্তরঃ গুজরাতের ভােগাবােরা নদীর তীরে
২৬. হরপ্পা সভ্যতায় কীরকম পাথর ও ধাতুর ভাস্কর্য দেখতে পাওয়া যায় ?
উত্তরঃ ব্রোঞ্জের তৈরি পশু মূর্তি, পােড়ামাটির নারীমূর্তি, পাখির মূর্তি।
২৭. হরপ্পাবাসীরা রােজকার ব্যবহারের জন্য কীসের পাত্র ব্যবহার করত?
উত্তরঃ মাটির তৈরি পাত্র ব্যবহার করত।
২৮. হরপ্পা সভ্যতার প্রধান দুটি কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করাে।
উত্তরঃ হরপ্পা, কালিবঙ্গান।
২৯. কে কত খ্রিস্টাব্দে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর বিস্তারিত বিবরণ দেন?
উত্তরঃ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে, জন মার্শাল।
৩০. হরপ্পা সভ্যতা কী ধরনের সভ্যতা।
উত্তরঃ হরপ্পা সভ্যতা নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা।
২১. হরপ্পা সভ্যতায় কী কী রপ্তানি করা হত?
উত্তরঃ বার্লি, ময়দা, তেল ও পশমজাত দ্রব্য।
২২. হরপ্পা সভ্যতায় জলপথে যােগাযােগের মাধ্যম কী ছিল?
উত্তরঃ বলদ, গাধা ও উট।
২৩. হরপ্পা সভ্যতায় সমাধি কোথায় পাওয়া গেছে?
উত্তরঃ কালিবঙ্গানে।
২৪. সিলমােহর তৈরির জন্য সিন্ধু সভ্যতার লােকেরা সাধারণত কোন ধরনের পাথর ব্যবহার করত?
উত্তরঃ স্টিটাইট নামে এক ধরনের পাথর।
২৫. লােথাল বন্দর কোথায় অবস্থিত?
উত্তরঃ গুজরাতের ভােগাবােরা নদীর তীরে
২৬. হরপ্পা সভ্যতায় কীরকম পাথর ও ধাতুর ভাস্কর্য দেখতে পাওয়া যায় ?
উত্তরঃ ব্রোঞ্জের তৈরি পশু মূর্তি, পােড়ামাটির নারীমূর্তি, পাখির মূর্তি।
২৭. হরপ্পাবাসীরা রােজকার ব্যবহারের জন্য কীসের পাত্র ব্যবহার করত?
উত্তরঃ মাটির তৈরি পাত্র ব্যবহার করত।
২৮. হরপ্পা সভ্যতার প্রধান দুটি কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করাে।
উত্তরঃ হরপ্পা, কালিবঙ্গান।
২৯. কে কত খ্রিস্টাব্দে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর বিস্তারিত বিবরণ দেন?
উত্তরঃ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে, জন মার্শাল।
৩০. হরপ্পা সভ্যতা কী ধরনের সভ্যতা।
উত্তরঃ হরপ্পা সভ্যতা নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা।
◈ আরো পড়ুনঃ ◈
❐ শূন্যস্থান পূরণ করাে :
১. মেহেরগড় সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়_____সালে।(ক) ১৯৬৪ সালে
(খ) ১৯৭৪ সালে
(গ) ১৯৮৪ সালে
উত্তরঃ (i) - 🅒 (ii) - 🅔 (iii) - 🅐 (iv) - 🅓 (v) - 🅑
(ঘ) কোনােটিই নয়
২. হরপ্পায় নগরগুলির নীচু বসতি এলাকাটা থাকত______অংশে।
(ক) পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব
(খ) উত্তর ও দক্ষিণ
২. হরপ্পায় নগরগুলির নীচু বসতি এলাকাটা থাকত______অংশে।
(ক) পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব
(খ) উত্তর ও দক্ষিণ
(গ) পশ্চিম ও পশ্চিম-পূর্ব
(ঘ) উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব
৩. হরপ্পা সভ্যতার____ টি সিলমােহর পাওয়া গেছে মেসোপটেমিয়ায়।
(ক) চব্বিশটা
(খ) তেইশটা
(গ) বত্রিশটা
৩. হরপ্পা সভ্যতার____ টি সিলমােহর পাওয়া গেছে মেসোপটেমিয়ায়।
(ক) চব্বিশটা
(খ) তেইশটা
(গ) বত্রিশটা
(ঘ) পঁচিশটা
৪. হরপ্পায়______গাছকে দেবতা হিসেবে পুজো করা হত।
(ক) শিমূলগাছ
(খ) বেলগাছ
(গ) অশ্বত্থ গাছ
৪. হরপ্পায়______গাছকে দেবতা হিসেবে পুজো করা হত।
(ক) শিমূলগাছ
(খ) বেলগাছ
(গ) অশ্বত্থ গাছ
(ঘ) কদম গাছ
৫. ভারতীয় উপমহাদেশে হরপ্পা সভ্যতাতেই প্রথম_____ গড়ে উঠেছিল।
(ক) নগর
(খ) গ্রাম
(গ) শহর
(খ) গ্রাম
(গ) শহর
(ঘ) শিল্প
৬. সিন্ধু সভ্যতার অপর নাম_____সভ্যতা।
(ক) মেহেরগড়
(ক) মেহেরগড়
(খ) হরপ্পা
(গ) বৈদিক
(ঘ) কোনােটিই নয়
❐ বামদিকের সঙ্গে ডানদিকের স্তম্ভ মেলায় :
| ক - স্তম্ভ | খ - স্তম্ভ |
|---|---|
| (i) মেহেরগড় সভ্যতার আবিষ্কারক | 🅐 আসকো পারপােলা |
| (ii) হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কারক | 🅑 শ্রেষ্ঠী |
| (iii) মেহেরগড় সভ্যতার কালসীমা নির্ধারণকারী | 🅒 ড. জাঁ ফ্রাঁসােয়া জারিজ |
| (iv) 'মহেনজোদারাে’ শব্দের অর্থ | 🅓 মৃতের স্তুপ |
| (v) সিন্ধুর বণিক | 🅔 রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় |
উত্তরঃ (i) - 🅒 (ii) - 🅔 (iii) - 🅐 (iv) - 🅓 (v) - 🅑
❐ হরপ্পা সভ্যতা ও মেহেরগড় সভ্যতার মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো :
| হরপ্পা সভ্যতা | মেহেরগড় সভ্যতা |
|---|---|
| ❶ হরপ্পা সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। | ❶ মেহেরগড় সভ্যতা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। |
| ❷ এই সভ্যতাটি পাঞ্জাব,গুজরাত,সৌরাষ্ট্র, রাজপুতানা, বেলুচিস্তান-এর মেহেরগড় মাকরান পর্যন্ত অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। | ❷ বালুচিস্তানে বােলান গিরিপথের ধারে প্রায় ৫০০ একর জুড়ে মেহেরগড় প্রত্নক্ষেত্রের অবস্থান ছিল। |
❐ শুদ্ধ বা অশুদ্ধ নির্ণয় করাে :
১. হরপ্পার মানুষ নানারকম জীবজন্তু গাছপালার পুজো করত।
১. হরপ্পার মানুষ নানারকম জীবজন্তু গাছপালার পুজো করত।
২. প্রত্নতাত্ত্বিকেরা হরপ্পার বিভিন্ন কেন্দ্রে পােড়ামাটির পুরুষ মূর্তি
পেয়েছেন।
৩. মহেনজোদাড়ােয় একটা পুরুষের মূর্তি পাওয়া গেছে।
৪. হরপ্পাকে তামা ও লােহা যুগের সভ্যতাও বলা হয়।
৫. হরপ্পা সভ্যতায় মৃতদেহ সমাধি দেওয়া হত।
৬. মেহেরগড় সভ্যতা আবিষ্কার করেন দয়ারাম সাহানি।
৭. হরপ্পা সভ্যতার নগরের উচু এলাকাকে বলা হয় সিটাডেল।
৮. হরপ্পা সভ্যতায় একুশটি সিলমােহর পাওয়া গেটে মেসােপটেমিয়ায়।
উত্তরঃ ১.শুদ্ধ ২.অশুদ্ধ ৩.শুদ্ধ ৪.অশুদ্ধ ৫.শুদ্ধ ৬.অশুদ্ধ ৭.শুদ্ধ ৮.অশুদ্ধ
উত্তরঃ ১.শুদ্ধ ২.অশুদ্ধ ৩.শুদ্ধ ৪.অশুদ্ধ ৫.শুদ্ধ ৬.অশুদ্ধ ৭.শুদ্ধ ৮.অশুদ্ধ
❐ সংক্ষেপে উত্তর দাও :
১. সিন্ধু সভ্যতার কৃষিকাজ সংক্ষেপে বর্ণনা করাে।
উত্তরঃ সিন্ধু নদের তীরে উর্বর জমিতে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। কৃষিকাজ ছিল এই সভ্যতার প্রধান পেশা। কৃষিতে তারা বেশ উন্নতও ছিল। নদীর ধারে গড়ে ওঠার ফলে সিন্ধু সভ্যতায় জমি ছিল উর্বর, ফসল ছিল খুব ভালাে। প্রতি বছর বর্ষার পরে বন্যা হত। বন্যার জল নেমে যাওয়ার পর পলিসমৃদ্ধ জমিতে বীজ বপন করা হত। চাষের জন্য কাঠের লাঙল ব্যবহার করা হত এবং ফসল কাটার জন্য পাথর ও ব্রোঞ্জের কাস্তে। প্রধান কৃষিজাত ফসল ছিল গম, যব ও জোয়ার। এর সঙ্গে ছিল ছােলা, মটর, সরষে, মশুর ডাল, ধান, তিল ও তুলাে। ভবিষ্যতের জন্য হরপ্পাবাসী শস্য সঞ্চয় করত। ধ্বংসাবশেষ থেকে কয়েকটি বড়াে শস্যাগারের। নিদর্শন পাওয়া গেছে। গ্রামের লােকেরা গােরু, ছাগল ও ভেড়া পালন করত।
উত্তরঃ সিন্ধু নদের তীরে উর্বর জমিতে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। কৃষিকাজ ছিল এই সভ্যতার প্রধান পেশা। কৃষিতে তারা বেশ উন্নতও ছিল। নদীর ধারে গড়ে ওঠার ফলে সিন্ধু সভ্যতায় জমি ছিল উর্বর, ফসল ছিল খুব ভালাে। প্রতি বছর বর্ষার পরে বন্যা হত। বন্যার জল নেমে যাওয়ার পর পলিসমৃদ্ধ জমিতে বীজ বপন করা হত। চাষের জন্য কাঠের লাঙল ব্যবহার করা হত এবং ফসল কাটার জন্য পাথর ও ব্রোঞ্জের কাস্তে। প্রধান কৃষিজাত ফসল ছিল গম, যব ও জোয়ার। এর সঙ্গে ছিল ছােলা, মটর, সরষে, মশুর ডাল, ধান, তিল ও তুলাে। ভবিষ্যতের জন্য হরপ্পাবাসী শস্য সঞ্চয় করত। ধ্বংসাবশেষ থেকে কয়েকটি বড়াে শস্যাগারের। নিদর্শন পাওয়া গেছে। গ্রামের লােকেরা গােরু, ছাগল ও ভেড়া পালন করত।
২. মহেঞ্জোদাড়াের স্নানাগার ও হরপ্পার শস্যাগারের পরিচয় দাও।
উত্তরঃ মহেঞ্জোদাড়ােতে আবিষ্কৃত স্নানাগারটি দৈর্ঘ্যে ১২ মিটার ও প্রস্থে ৭ মিটার এবং গভীরতায় ২.৫ মিটারের মতাে ছিল। পুরাে স্নানাগারটি উৎকৃষ্ট পােড়ামাটির ইটের গাঁথনি দিয়ে তৈরি এবং ইটগুলির খাঁজে ছিল শিলাজতু নামক জলনিরােধক পদার্থের প্রলেপ। স্নানাগারটির মেঝেতে ছিল জল নিরােধক প্লাস্টারের প্রলেপ। স্নানাগারটির একটি কোণের দিকে মেঝের ঢাল ছিল এবং সেই কোণে ছিল জল। বেরিয়ে যাওয়ার নর্মা। ওঠা নামার জন্য স্নানাগারটির উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে দুটি ইটের সিঁড়ি ছিল। হরপ্পায় একটি প্রকাণ্ড উঁচু ইটের বেদির উপর একটি বিশাল একতলা বাড়ি পাওয়া গেছে। এটি ঠিক কী তা নিয়ে কিছু মতভেদ আছে। তবে প্রত্নবিজ্ঞানীরা এটিকে শস্যগার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বাড়িটির দুদিকে ছটা করে ঘর আছে। এতে হাওয়া চলাচলের জন্য ঘুলঘুলি আছে, যাতে খাদ্যশস্য শুকনাে ও তাজা সম্ভব হয়।
৩. হরপ্পার কারিগরি শিল্প সম্পর্কে সংক্ষেপে আলােচনা করাে।
উত্তরঃ হরপ্পা সভ্যতার নানারকম মাটির পাত্র ছিল কারিগরির উন্নতির নজির। পােড়ানাের ফলে সেগুলি লালচে রঙের হয়ে উঠেছিল। পাত্রের গায়ে উজ্জ্বল কালাে রঙের নকশাও আঁকা হত। মাটির পাত্র হালকা ও পাতলা হওয়ায় রােজকার কাজে ব্যবহার হত। মাটি দিয়ে থালা, বাটি, রান্নার বাসন হরপ্পা সভ্যতায় তৈরি হত। তামা, ব্রোঞ্জ ও কাসার তৈরি জিনিসপত্র তৈরি ও বিক্রির চল ছিল। তামার ও পাথরের তৈরি ছুরি, কুঠার, বাটালি প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে। হরপ্পা সভ্যতায় কাপড় বােনার কারিগরও ছিল। কাপড়ে সুতাের কাজ করার শিল্পও হরপ্পা সভ্যতায় দেখা যায়। ইট বানানাের শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সােনা, তামা, শাঁখ, দামি-কমদামি পাথর, হাতির দাঁত প্রভৃতির গয়না তৈরির কারিগর ছিল। নীলচে পালিস লাজুলি পাথরও গয়না বানাতে লাগত। মালার দানা বানানাের কারখানাও হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া গেছে। সূক্ষ্ম ওজন মাপার বাটখারারও খোঁজ মিলেছে।
উত্তরঃ হরপ্পা সভ্যতার নানারকম মাটির পাত্র ছিল কারিগরির উন্নতির নজির। পােড়ানাের ফলে সেগুলি লালচে রঙের হয়ে উঠেছিল। পাত্রের গায়ে উজ্জ্বল কালাে রঙের নকশাও আঁকা হত। মাটির পাত্র হালকা ও পাতলা হওয়ায় রােজকার কাজে ব্যবহার হত। মাটি দিয়ে থালা, বাটি, রান্নার বাসন হরপ্পা সভ্যতায় তৈরি হত। তামা, ব্রোঞ্জ ও কাসার তৈরি জিনিসপত্র তৈরি ও বিক্রির চল ছিল। তামার ও পাথরের তৈরি ছুরি, কুঠার, বাটালি প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে। হরপ্পা সভ্যতায় কাপড় বােনার কারিগরও ছিল। কাপড়ে সুতাের কাজ করার শিল্পও হরপ্পা সভ্যতায় দেখা যায়। ইট বানানাের শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সােনা, তামা, শাঁখ, দামি-কমদামি পাথর, হাতির দাঁত প্রভৃতির গয়না তৈরির কারিগর ছিল। নীলচে পালিস লাজুলি পাথরও গয়না বানাতে লাগত। মালার দানা বানানাের কারখানাও হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া গেছে। সূক্ষ্ম ওজন মাপার বাটখারারও খোঁজ মিলেছে।
৪. সিন্ধুসভ্যতার সামাজিক শ্রেণিবিভাগের পরিচয় দাও।
উত্তরঃ সিন্ধুসভ্যতার লিপি যেহেতু আজও উদ্ধার করা যায়নি। তাই এই সভ্যতার সমাজ জীবন সম্পর্কেও বিশেষ কিছু জানা যায়নি। অবশ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে এই সভ্যতার সামাজিক শ্রেণিবিভাজন সম্পর্কে কিছু আনন্দাজ করা গেছে। নীচে সে সম্পর্কেও উল্লেখ করা হল—উচ্চশ্রেণি : এই সভ্যতায় একটি উচ্চশ্রেণি বা শাসকশ্রেণি ছিল। সম্ভবত পুরােহিত, অভিজাত ও ধনী ব্যবসায়ীরা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কৃষক : এই সভ্যতার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ ছিল কৃষিজীবী। এরা থাকত শহরের বাইরে গ্রামগুলিতে। কারিগর : এই শ্রেণির মধ্যে ছিল কুমাের, কামার, ছুতাের ও তাতি, বণিক।
দোকানদার : খুব ধনী ব্যবসায়ীরা উচ্চশ্রেণির অন্তর্গত হলেও অনেক মাঝারি ব্যবসায়ী এবং দোকান দারও ছিল। শ্রমিক : ব্যবসায়ী ও কারিগরদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করার জন্য একটি শ্রমিক শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। বেতনের বিনিময়ে কাজ করা এই মানুষগুলি স্বাভাবিকভাবেই গরিব ছিল। শহরগুলির প্রান্তে খুব ছােটো ছােটো যে বাসস্থানগুলি পাওয়া গেছে। সেখানেই সম্ভবত তারা থাকত।
৫. সিন্ধু-সভ্যতা পতনের কারণ কী?
উত্তরঃ সিন্ধু সভ্যতা পতন কেন হল সে বিষয়ে আজও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। নীচে পতনের সম্ভাব্য কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হল।
(ক) বহিঃশত্রুর আক্রমণ : একটা সময় ইতিহাসবিদরা মনে করতেন, বহিঃশত্রুর, বিশেষত আর্যদের আক্রমণে এই সভ্যতাটি ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু আজকাল ইতিহাসবিদরা এই ধারণাটি পােষণ করেন না কারণ বহিঃশত্রুর আক্রমণের নিদর্শন খুঁজে পাননি প্রত্নবিদরা।
(খ ) জলবায়ুর পরিবর্তন : প্রত্নবিজ্ঞানীরা মনে করেছেন ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর থেকে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কমে যায় ফলে কৃষিজ ফলনও কমে এভাবে সভ্যতাটির ক্রমপতন ঘটে।
(গ) বন্যা : এই অঞ্চলে নদীগুলিতে পলি পড়ে জলধারণ ক্ষমতা কমে যায় ফলে প্রতিবছর বন্যা হয়। এটিও পতনের কারণ হতে পারে।
(ঘ ) পরিবেশ ধ্বংস : মাটি পােড়ানাের জন্য ইটের তৈরিতে কাঠের প্রয়ােজন তার জন্য প্রচুর গাছ কেটে ফেলায় আবহাওয়া শুকনাে হয়ে যায়। সভ্যতাটি পতনের দিকে এগিয়ে যায়।
৬. হরপ্পার বাণিজ্য সম্পর্কে লেখাে৷
উত্তরঃ হরপ্পা সভ্যতার তেইশটা সিলমােহর মেসােপটেমিয়ায় পাওয়া যায়। এর থেকে বােঝা যায় যে, মেসােপটেমিয়ার সঙ্গে এই সভ্যতার বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল। জলপথের মাধ্যমে বাণিজ্যিক যােগাযােগ গড়ে ওঠে। বিদেশ থেকে হরপ্পা সভ্যতায় সােনা, রুপাে, তামা, দামি পাথর, হাতির দাঁতের চিরুনি, পাখির মূর্তি আমদানি করা হত আর বালি, ময়দা, তেল ও পশমজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হত। ইরানেও তুর্কমেনিস্তানে বাণিজ্যিক যােগাযােগের নিদর্শন পাওয়া যায়। বলদ, গাধা ও উটের মাধ্যমে স্থলপথের বাণিজ্যিক যােগাযােগ ছিল। হরপ্পার রাস্তায় গাড়ির চাকার ছাপও পাওয়া যায়। পশুতে টানা গাড়ি ব্যবহার হত। জলপথে নৌকার ব্যবহার অনেক সুবিধে ছিল। পালতােলা নৌকার ব্যবহার হরপ্পায় ছিল। হরপ্পার অর্থনীতি ও যাতায়াত ব্যবস্থা অনেকটাই নদীর উপর নির্ভর করত।
৭. সভ্যতার নানাদিক বলতে কী বােঝাে?
উত্তরঃ সভ্যতার নানাদিকবলতে সাধারণত বােঝায় উন্নত গ্রাম ও নগরজীবন, লিপি, শিল্প ও স্থাপত্য এবং মাসিক কাঠামাে।
৮. কোন যুগের মানুষ তামার সূক্ষ্ম হাতিয়ার তৈরি করল?
উত্তরঃ অনেকেই অনুমান করেন যে, নতুন পাথরের যুগের শেষভাগ থেকে মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখেছিল। তারা পাথরের বদলে তামার হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে লাগল। তামা সহজে পাওয়া যেত এবং তা গলানাে সহজ ছিল।
৯. তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ কাকে বলা হয়?
উত্তরঃ আজ থেকে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে পর্যন্ত মানুষ তামার ব্যবহার করেছিল। কিন্তু মানুষ একদিন তামার থেকেও শক্ত ধাতুর প্রয়ােজনীয়তা অনুভব করল। খ্রিস্টজন্মের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মানুষ তামা ও টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ আবিষ্কার করল। এই সময়-কালকেই বলে তাম্রব্রোঞ্জ যুগ।
১০. কোন সময় মানুষ স্থায়ী বসবাস গড়ে তুলল?
উত্তরঃ পাথরের যুগের শেষ দিকে মানুষ আর খাবারের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানাে পছন্দ করল না। তারা এবার স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে দিল। নিজেদের খাদ্য নিজেরাই উৎপাদন করতে শিখল। শুরু করে দিল পশুপালন বদলে গেল মানুষের জীবন।
১১. কবে থেকে মানুষের মধ্যে কেনাবেচা শুরু হল?
উত্তরঃ নতুন পাথরের যুগে মানুষ যখন ঘরবাড়ি বাধল, চাষবাস শুরু করল, তখন সে
একটু একটু করে সভ্য হল। সভ্য মানুষদের নানা জিনিসের চাহিদা বেড়ে গেল সমস্যা
দেখা দিল তখনই। অর্থাৎ, কোনাে মানুষ একাই সব কিছু তৈরি করতে পারে না। ফলে
শুরু হল জিনিস দিয়ে জিনিস দেওয়া-নেওয়া। এরপর তারা তৈরি করল মুদ্রা ।
সহজ হয়ে গেল কেনাবেচা।
১২.মেহেরগড় সভ্যতাকে কোন নতুন পাথরের যুগ বলে চিহ্নিত করা যায়?
উত্তরঃ ১৯৭৪ সালে আগেকার পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে মেহেরগড়ে তামা ও পাথরের যুগের একটি প্রত্নকেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। মেহেরগড় নামক স্থানটি বােলান গিরিপথ থেকে খানিক দূরে অবস্থিত। সেখানে মূলত একটি কৃষিনির্ভর সভ্যতার নজির পাওয়া গেছে। মেহেরগড়ের মানুষ পাথরের যন্ত্রপাতিই প্রধানত ব্যবহার করত। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করেন, মেহেরগড় সভ্যতার শেষ দিকে মানুষ তামার ব্যবহারও শিখে যায়। সময়টা ছিল প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৪৩০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৩৮০০ অব্দ পর্যন্ত।