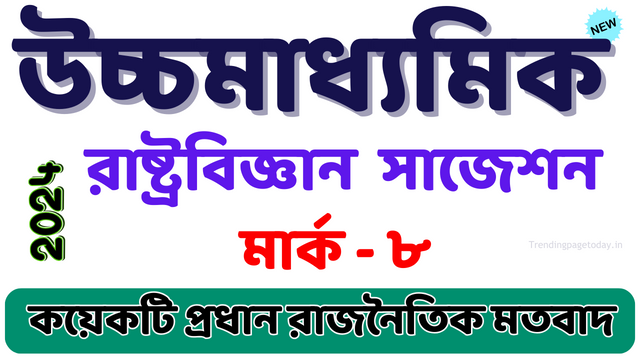❏ কয়েকটি প্রধান রাজনৈতিক মতবাদ
✱ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: প্রতিটি প্রশ্নের মান-৮
1. কার্ল মার্কস-এর রাষ্ট্র সম্পর্কিত তত্ত্বটি আলোচনা করো।
2. কার্ল মার্কস-এর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বটি আলোচনা করো।
3. দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলতে কী বোঝো? দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বিষয়ে মার্কসের ধারণা বিশ্লেষণ করো।
4. “আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তা হল শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস” ব্যাখ্যা করো।
5. গান্ধিজির ‘সত্যাগ্রহ’ সম্পর্কিত ধারণাটি আলোচনা করো।
1. কার্ল মার্কস-এর রাষ্ট্র সম্পর্কিত তত্ত্বটি আলোচনা করো।
▢ ভূমিকা : রাষ্ট্রবিচিন্তার ইতিহাসে কার্ল মার্কসকে সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের জনক হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। মার্কস তাঁর পূর্বসূরীদের অন্ধভাবে অনুসরণ না করে তাঁদের চিন্তা-ভাবনার সমালোচনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এমন একটি তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করেন, মানব সভ্যতার ইতিহাসে যা মার্কসবাদ নামে পরিচিত। লেনিনকে অনুসরণ করে একথা বলা যায় যে, মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষাকেই মার্কসবাদ নামে অভিহিত করা যায়। মনে রাখতে হবে হবে যে, মার্কসবাদ শুধু একটা তাত্ত্বিক ধারণা বা যান্ত্রিক মতবাদ নয়, মার্কসবাদ হলো নিরন্তর বিকশিত ও গতিশীল একটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ। এই মতবাদকে শক্তিশালী তত্ত্বে পরিণত করতে এবং বৌদ্ধিক জগতে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে যেহেতু মার্কস অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন সেহেতু তাঁকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।
▢ কার্ল মার্কস-এর রাষ্ট্র সম্পর্কিত তত্ত্ব : মার্কসীয় মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের আবির্ভাব আকস্মিকভাবে ঘটেনি। উৎপাদন ব্যবস্থার প্রকৃতিগত পরিবর্তনের ফলে সমাজবিবর্তনের একটি বিশেষ অধ্যায়ে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই সময়ে সমাজ সম্পত্তিবান শোষকশ্রেণি এবং সম্পত্তিহীন শোষিতশ্রেণি, এই দুই পরস্পরবিরোধী শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মার্কসের মতে, সম্পত্তি-মালিকানার নিরাপত্তার জন্য যে বলপ্রয়োগমূলক হাতিয়ারের প্রয়োজন হয় তা হল রাষ্ট্র। রাষ্ট্র নামক হাতিয়ারের সাহায্যে সমাজে প্রভুত্বকারী সংখ্যালঘু সম্পত্তিবান শ্রেণি তার বিরোধী সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্পত্তিহীন শ্রেণিকে শোষণ করে। এভাবে দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ ও পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্র উৎপাদন-ব্যবস্থার মালিকদের স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠকে শোষণ করার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।
মার্কসের মতে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ধ্বংসের ফলে ‘সর্বহারার একনায়কত্ব’ প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হবে। রাষ্ট্র সেখানে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে না, বরং সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি রচনা করবে। সাম্যবাদী সমাজে সবরকম শ্রেণিশোষণের সমাপ্তি ঘটার ফলে রাষ্ট্রযন্ত্রের কোনো প্রয়োজন থাকবে না। তখন স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটবে।
2. কার্ল মার্কস-এর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বটি আলোচনা করো।
▢ ভূমিকা : রাষ্ট্রবিচিন্তার ইতিহাসে কার্ল মার্কসকে সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রের জনক হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। মার্কস তাঁর পূর্বসূরীদের অন্ধভাবে অনুসরণ না করে তাঁদের চিন্তা-ভাবনার সমালোচনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এমন একটি তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করেন। এমিল বার্নসের মতে, মার্কসবাদ হল আমাদের এই জগৎ এবং তারই অংশ মানবসমাজ সম্বন্ধে সাধারণ তত্ত্ব। এর নামকরণ হয়েছে কার্ল মার্কস-এর (১৮১৮ – ১৮৮৩ খ্রি.) নামানুসারে। মার্কস-এর ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বটি সম্পর্কে বিস্তারিত নিচে আলোচনা করা হলো —
▢ মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ : মানবসমাজের বিকাশের প্রকৃতি ও ইতিহাস বিশ্লেষণে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী তত্ত্বের প্রয়োগ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলে পরিচিত। কার্ল মার্কস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন। ডারউইন যেমনভাবে জীবজগতের বিবর্তনের নীতি আবিষ্কার করেছিলেন, মার্কসও তেমনি মানব ইতিহাসের বিবর্তনের মূল সূত্র বিজ্ঞানসম্মতভাবে আবিষ্কার করেছিলেন। মার্কসের কাছে ইতিহাস কয়েকটি ঘটনার সংকলন অথবা কাহিনির বিবরণ নয়। মানবসমাজের ইতিহাস আবশ্যিকভাবেই শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস, শ্রেণিশোষণ ও দমনের ইতিহাস। মরিস কর্নফোর্থের মতে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তিনটি মূল সূত্র রয়েছে। সেগুলি হল – সমাজের পরিবর্তন ও বিকাশ প্রকৃতির মতো সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ও সমাজের বৈষয়িক জীবনের বিকাশের ওপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক তত্ত্ব, মতাদর্শ, সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ও বৈষয়িক জীবন থেকে যেসব মতাদর্শ ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, বাস্তবে সেগুলি বৈষয়িক জীবনের বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।
[1] মানবসমাজের মৌলিক পরিবর্তন ও উৎপাদন পদ্ধতি: মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের German Ideology শীর্ষক রচনায় লিখেছেন, মানুষের অস্তিত্বের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হল খাদ্য, পানীয়, পরিধেয় ও বাসস্থান। জীবনযাপনের এই বাস্তব প্রয়োজনগুলি পূরণের জন্য মানুষ প্রথমে উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করে। মার্কসের মতে, রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, প্রভৃতি চিন্তাধারা নয়, মানুষের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলির উৎপাদন পদ্ধতি রয়েছে মানবসমাজের পরিবর্তনের মূলে।
[2] ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর ধারণা: মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূলে রয়েছে ভিত্তি (Basis) ও উপরিকাঠামোর (Super structure) ধারণা। উৎপাদন পদ্ধতি এবং উৎপাদন সম্পর্ককে নিয়ে যে অর্থনৈতিক কাঠামো তা-ই হল সমাজের মূল ভিত্তি বা বুনিয়াদ (Basis)। এই ভিত্তি বা বুনিয়াদের ওপরে গড়ে ওঠা সামাজিক সম্পর্ক, মতাদর্শ ও প্রতিষ্ঠান হল উপরিকাঠামো (Super structure)
[3] উৎপাদন পদ্ধতির গুরুত্ব : ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুসারে, মানবসমাজের বিকাশের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদন পদ্ধতি। এই উৎপাদন পদ্ধতি সবকিছুর মূল। তাই ইতিহাসকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে উৎপাদন পদ্ধতির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রসঙ্গত বলা যায়, মার্কসীয় তত্ত্বে উৎপাদন বলতে সবসময় সামাজিক উৎপাদনকে বোঝানো হয়েছে। সমাজবিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে উৎপাদন পদ্ধতি। সমাজের কাঠামো এই উৎপাদন পদ্ধতির প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। তাই উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে সমাজব্যবস্থাও পরিবর্তিত হয়।
[4] উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের ইতিহাস: মার্কসীয় মতবাদ অনুসারে,মানবসমাজের বিকাশের ইতিহাস হল উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের ইতিহাস। মানবসমাজের পরিবর্তনের মুখ্য কারণ হল উৎপাদন শক্তি ও উপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব। মার্কসের বক্তব্য হল, নতুন উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক পুরোনো ব্যবস্থার ধবংসের ফলে আলাদাভাবে সৃষ্টি হয় না। পুরোনো ব্যবস্থার মধ্যেই নুতন উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত হয়। Capital গ্রন্থে মার্কস বলেন, প্রত্যেক সমাজব্যবস্থার গর্ভে যখন নতুন সমাজের উদ্ভব হয়, শক্তি তখন ধাত্রী হিসেবে কাজ করে (“Force is the midwife of every old society pregnant with a new one”) । মার্কসীয় মতবাদ অনুযায়ী, উৎপাদন শক্তির বিকাশ একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে। কিন্তু সেই স্তরের পরে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের ধারকশ্রেণি নতুন উৎপাদন শক্তির বিকাশে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন বিনা বাধায় সাধিত হয় না। পুরোনো উৎপাদন সম্পর্ককে বাতিল করার জন্য প্রয়োজন হয় নতুন প্রগতিশীল মতাদর্শ। সেই সময় মানুষের সচেতন কর্মকাণ্ড, অগ্রগতির
স্বতঃস্ফূর্ত কারণ হিসেবে কাজ করে। ধীরগতি বিবর্তনের বদলে দেখা দেয় বিপ্লব।
[5] সমাজবিবর্তনের বিজ্ঞানসঙ্গত ধারা: মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারে, আদিম যৌথ সমাজজীবনে উৎপাদনের উপাদানের মালিক ছিল সমগ্র মানবসমাজ। উৎপাদনের উপাদানের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকায় সে সময় শ্রেণিশোষণ ছিল না | দাস সমাজব্যবস্থায় দাসমালিকরা ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম করে। ক্রমে সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের মালিক হল সামন্তপ্রভুরা। এসময় উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকরা ছিল ভূমিদাস। তখনকার সমাজব্যবস্থার সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্ক যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ ছিল। পরে কৃষির উন্নতির পাশাপাশি যন্ত্রশিল্পের উদ্ভব ঘটলে সামন্তসমাজের শোষণমূলক উৎপাদন সম্পর্ক যন্ত্রশিল্পের বিকাশে বাধা দেয়। এর ফলে সামন্তসমাজের অবসান ঘটে এবং পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। পুঁজিবাদী সমাজের ধনিকশ্রেণি উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা দখল করে। শ্রমিকরা জীবনধারণের জন্য পুঁজিপতিদের কাছে শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়।
3. দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলতে কী বোঝো? দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বিষয়ে মার্কসের ধারণা বিশ্লেষণ করো।
▢ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ : দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হল মার্কসীয় তত্ত্বের প্রধান ভিত্তি। মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক ভাববাদ থেকে উপাদান গ্রহণ করলেও তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল বক্তব্য হল জগৎ প্রকৃতিগতভাবে বস্তুময়। জগতের প্রতিটি বস্তু পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল ও পরস্পরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
▢ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বিষয়ে মার্কসের ধারণা :
(i) বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব : দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বিশ্বাস করে যে, প্রতিটি বস্তু ও ঘটনার মধ্যে পরস্পরবিরোধী ধর্ম একই সঙ্গে অবস্থান করে। তার ফলে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। যেমন পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিমালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সমাজ পরিবর্তনের মূল কারণ হিসেবে কাজ করে।
(ii) পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন : দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুসারে বিপরীতধর্মী শক্তিগুলির দ্বন্দ্বের ফলে বস্তুজগতে পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন ঘটে। এই গুণগত পরিবর্তন বস্তুর আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। মার্কসের মতে, পুঁজিবাদী সমাজের পরিমাণগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় আকস্মিকভাবে বিপ্লবের মাধ্যমে যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে তার ফলে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পত্তন হয়। এভাবে সমাজের পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন ঘটে।
(iii) অস্বীকৃতির অস্বীকৃতি : দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতে পুরাতনের অস্বীকৃতি ছাড়া নতুনের আবির্ভাব ঘটতে পারে না। নতুন ক্রমে পুরোনো হয়।তখন তারও বদল ঘটে। এভাবে দাস সমাজব্যবস্থাকে অস্বীকার করে সামন্ত সমাজের বিকাশ, সামন্ত সমাজকে অস্বীকার করে পুঁজিবাদের বিকাশ, আবার পুঁজিবাদকে অস্বীকার করে সমাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটে।
▢ উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, রাষ্ট্রপ্রকৃতি মার্কসীয় তত্ত্বের স্বতন্ত্র গুরুত্ব রয়েছে। এই তত্ত্বে শ্রেণিদ্বন্দ্বের যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা উপেক্ষা করা যায়নি। অর্থনৈতিক কারণ সব দ্বন্দ্বের মূল কারণ না হলেও, এর গুরুত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই । ল্যাস্কির ভাষায় বলা যায়, পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রে যেখানে মানুষ সামাজিক উন্নতিবিধানের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে, সেখানে মার্কস সর্বদা প্রেরণা ও ভবিষ্যদ্বাণীর উৎস হিসেবে থেকে যাবেন (In every country of the world where men have set themselves to the task of social improvement, Marx has been always the source of inspiration and prophecy)।
4. “আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তা হল শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস”।—ব্যাখ্যা করো।
▢ ভূমিকা : এমিল বার্নস-এর মতে, একই প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, সমাজের এইরকম এক-একটি অংশ হল এক-একটি শ্রেণি। লেনিনের মতে, সমাজে শ্রেণি হল সেই সামাজিক গােষ্ঠীসমূহ যাদের মধ্যে কোনাে এক গােষ্ঠী অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিজ অবস্থানের জোরে অন্য কোনাে গোষ্ঠীর শ্রমকে আত্মসাৎ করে। লেনিনের এই সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়一 [1] শ্রেণি হল ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার্য এমন একটি বর্গ যা উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের একটি ফল। [2] শ্রেণি এমন একটি বর্গ যার অবস্থান নির্ধারিত হয় উৎপাদন ব্যবস্থার উপকরণগুলির সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। [3] সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণী চরিত্র নির্দেশিত হয় সমাজস্থ সম্পদ হস্তগত করার পদ্ধতি ও পরিমাণের উপর ভিত্তি করে।
▢ শ্রেণিসংগ্রাম : মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখা ‘দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’-র সূচনা বাক্যটি হল — ‘আজ পর্যন্ত (আদিম সাম্যবাদী সমাজের পর থেকে) যতগুলি সমাজ দেখা গেছে, তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস। ’ মার্কসীয় দর্শনে শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রেণি বলতে বোঝায় একই প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্বাহকারী সমাজের এক-একটি অংশ। যেমন— পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় যে গোষ্ঠী শ্রমদান করে, তাকে বলা হয় শ্রমিক শ্রেণি। মার্কসীয় মতে, বিনা সংগ্রামে বা সংঘাতে, মসৃণ পথে সমাজের পরিবর্তন ঘটে না, সমাজের বিকাশ ঘটে শ্রেণিসংগ্রামের ফলেই। তাই তাঁরা শ্রেণিসংগ্রামকে সমাজবিকাশের চালিকা শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। মার্কসীয় মত অনুসারে শ্রেণির বিভাজন দুই প্রকার—মুখ্য এবং গৌণ। যে শ্রেণিদের বাদ দিয়ে উৎপাদন-ব্যবস্থা চলতে পারে না তারা মুখ্যশ্রেণি । যেমন, পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণি আর অন্যরা হল গৌণ শ্রেণি। অতীতকালে শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল না।
মার্কসের মতে, পৃথিবীতে প্রথম শ্রেণিবিভক্ত সমাজ দেখা যায় দাস সমাজে এই সমাজে দুটি মুখ্য শ্রেণি ছিল দাস ও দাসমালিক। দাস সমাজেই শুরু হল এক শ্রেণি কর্তৃক অপর শ্রেণির শোষণ। এই সমাজে দাস ও দাসমালিকদের মধ্যে শ্রেণিদ্বন্দ্ব তীব্র হয়। দাস সমাজের পরবর্তী পর্যায়ে সমাজ বিভক্ত হয় শোষক সামন্তপ্রভু ও শোষিত ভূমিদাস শ্রেণিত। এই দুই শ্রেণির মধ্যে শ্রেণিদ্বন্দ্বও চলতে থাকে। এরপর গড়ে ওঠে পুঁজিবাদী সমাজ। এই সমাজ বুর্জোয়া ও সর্বহারা, এই দুই পরস্পরবিরোধী শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শ্রেণিদ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং সর্বহারা শ্রেণি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আদর্শগত সংগ্রাম চালাতে থাকে। মার্কসীয় মতে পুঁজিপতি বা বুর্জোয়া শ্রেণি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হলে সর্বহারার একনায়কত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শ্রেণিদ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে। পরিশেষে সাম্যবাদী সমাজে শ্রেণিহীন এবং শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে।
▢ উপসংহার : উপরোক্ত বিরূপ সমালােচনা সত্ত্বেও শ্রেণি ও শ্রেণিসংগ্রাম সম্পর্কে মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যকে কোনােমতেই অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন গৌণ শ্রেণির অস্তিত্ব সত্ত্বেও কোনাে সমাজে উৎপাদন সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পরবিরােধী দুটি মুখ্য শ্রেণির উপস্থিতি এবং তাদের মধ্যে শ্রেণিসংঘাতের ঘটনা হল ঐতিহাসিক সত্য। আবার সমাজে বিভিন্ন কারণে সৃষ্ট সংঘাতের মধ্যে অর্থনৈতিক সংঘাতই হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শ্রেণিসংগ্রামের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর তারাই সাধারণ মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং তখন থেকেই মানুষ সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে নিজেদের ইতিহাস রচনা করবে বলে মার্কসবাদী দাবি করেন। অ-মার্কসবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকাইভারও শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব কে উপেক্ষা করতে পারে না। তাই সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিবর্তনের ক্ষেত্রে শ্রেণিসংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।
5. গান্ধিজির ‘সত্যাগ্রহ’ সম্পর্কিত ধারণাটি আলোচনা করো।
▢ ভূমিকা : গান্ধিজির তত্ত্বের একটি অন্যতম প্রধান নীতি হল সত্যাগ্রহ। পণ্ডিতদের মতে, সত্য প্রতিষ্ঠায় জিশুর আত্মত্যাগ, গৌতম বুদ্ধের অহিংসা ও প্রেমের বাণী এবং রাস্কিন, থোরো ও টলস্টয়ের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গান্ধিজি সত্যাগ্রহ-সম্পর্কিত ধারণাটি গড়ে তোলেন। এর পাশাপাশি গীতা ও উপনিষদ সম্বন্ধে তাঁর গভীর অধ্যয়ন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ‘নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ’ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তাঁর সত্যাগ্রহ-সম্পর্কিত ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছিল। ‘সত্যাগ্রহ’ কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল সত্যের প্রতি আগ্রহ । সত্যাগ্রহ হল এক সুসংহত জীবনদর্শন, সত্য প্রতিষ্ঠার নৈতিক সংগ্রামে এক নিরস্ত্র প্রতিরোধ। পণ্ডিতরা গান্ধিজির সত্যাগ্রহকে ব্রিটিশরাজের বিপক্ষে চালিত রাজনৈতিক সংগ্রামের এক কৌশল বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে, এ হল অহিংস উপায়ে সংগ্রামের পথ। গান্ধিজি তাঁর হিন্দ স্বরাজ গ্রন্থে সত্যাগ্রহের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, “সত্যাগ্রহ হল ব্যক্তির আত্মপীড়নের মাধ্যমে স্বাধিকার অর্জনের এক প্রচেষ্টা।”
▢ গান্ধিজির ‘সত্যাগ্রহ’ সম্পর্কিত ধারণা : গান্ধিজি তাঁর রচনায় সত্যাগ্রহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যেসব দিকের কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—
[1] আত্মিক শক্তির সংগ্রাম : গান্ধিজির মতে, সত্যাগ্রহ হল আত্মিক শক্তির এক সংগ্রাম। এ হল এমন এক ধরনের সংগ্রাম যেখানে প্রচলিত অর্থে জয়পরাজয় বলে কিছু নেই। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই হল এই সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য।
[2] জন্মগত অধিকার: গান্ধিজি মনে করতেন, সত্যাগ্রহ হল মানুষের সহজাত জন্মগত অধিকার (Satyagraha is an inherent birth right of a person)। এ হল প্রতিটি মানুষের কাছেই জন্মগতভাবে এক অর্জিত অধিকার। এই কারণে গান্ধিজি একে পবিত্র অধিকার ও পবিত্র কর্তব্য বলে অভিহিত করেন।
[3] সত্যাগ্রহ ও প্রতিপক্ষ : প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘাতের পথে গিয়ে তার ওপর চরম আঘাত হানা সত্যাগ্রহের কাজ নয়। সত্যাগ্রহের পথ আলাদা। সেখানে অহিংসা, প্রেম ও ভালোবাসার সাহায্যে প্রতিপক্ষের হৃদয় জয় করাই হল মূল উদ্দেশ্য। তাই গান্ধিজি সত্যাগ্রহীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, এ কাজে অধৈর্য হলে চলবে না। অধৈর্য হওয়ার অর্থ হল হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা। অন্যায়কারী প্রতিপক্ষকে বিব্রত করার মনোভাব সত্যাগ্রহীর থাকা উচিত নয়।
[4] সত্যাগ্রহ দুর্বলের জন্য নয় : গান্ধিজি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন,সত্যাগ্রহে দুর্বলতা, ভীরুতা ও কাপুরুষতার কোনো জায়গা নেই। তাঁর মতে, যারা ভীরু, কাপুরুষ ও দুর্বল তারা আর যাই হোক সত্যাগ্রহী হতে পারবে না। সত্যাগ্রহ মানে সত্যকে জয় না করা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য। এই কাজ দুর্বল চিত্ত মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়।
[5] সত্যাগ্রহ ও অহিংসা: সত্যাগ্রহের সঙ্গে অহিংসার একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। সত্যাগ্রহী কখনও হিংসাকে প্রশ্রয় দেবে না। সে হবে অহিংসার পূজারি। প্রতিপক্ষকে সে যেমন ঘৃণা করবে না, তেমনি তাকে অতিরিক্ত শ্রদ্ধাও করবে না। এভাবে অহিংসা দিয়ে হিংসাকে জয় করার জন্য তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এ ছাড়া গান্ধিজি সত্যাগ্রহীদের আত্মপীড়নের জন্য তৈরি থাকতেও বলেছিলেন। তিনি মনে করতেন, অন্যায়ের প্রতিরোধ করার জন্য সত্যাগ্রহী আত্মবিসর্জন দিতেও বিন্দুমাত্র ভয় পাবে না।
[6] সত্যাগ্রহের বিধি : গান্ধিজি তাঁর রচনায় সত্যাগ্রহের বিধি সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছিলেন, “ভয় কাকে বলে সত্যাগ্রহী জানে না। অতএব প্রতিপক্ষকে বিশ্বাস করতে সে কখনোই শঙ্কিত হবে না। প্রতিপক্ষ তাকে যদি কুড়িবারও ঠকায়, তবুও একুশবারের বার সত্যাগ্রহী তাকে বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। কারণ সত্যাগ্রহের আদর্শের মূল কথা হল মানুষের প্রকৃতিতে নিয়ত আস্থা রাখা।”
[7] সত্যাগ্রহের চরিত্র : গান্ধিজি বলেছেন, সত্যাগ্রহের চরিত্রই হল সত্যাগ্রহের সৌন্দর্য, এটা আপনা-আপনিই আসে, এর সন্ধান করতে হয় না। নিরন্তর সত্যসন্ধান ও সত্যে উপনীত হওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্তের নামই সত্যাগ্রহ।
- উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস MCQ সাজেশন ২০২৪
- উচ্চমাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাজেশন ২০২৪
- উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাস সাজেশন ২০২৪ মার্ক - ৮
- উচ্চমাধ্যমিক সংস্কৃত সাজেশন ২০২৪