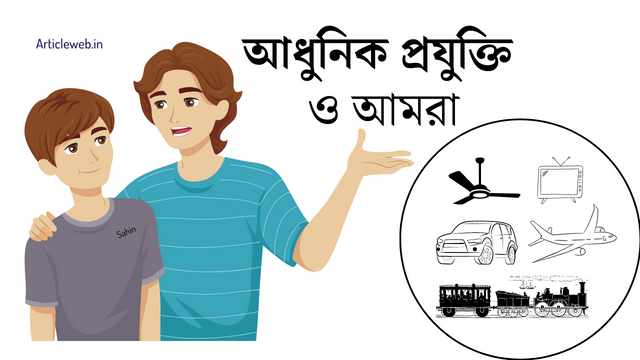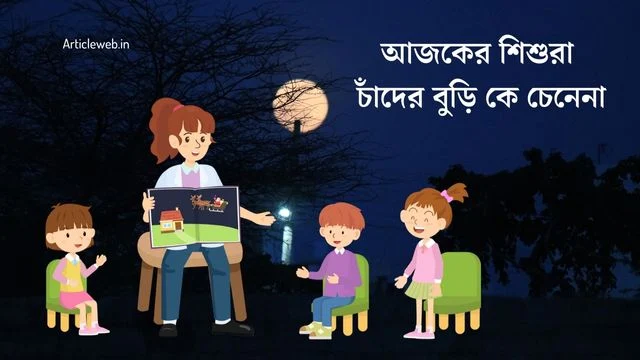Bangla Rachana total 10 | Amar Chokhe Amar Desh
❐ Table Of Contents :
আমার চোখে আমার দেশ
ロ “ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী....” স্বামী বিবেকানন্দের চোখে এই দেশই আমার দেশ। দেশকে দেখার মতো চোখ না থাকলে অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো দেশ মনের অগোচরে রয়ে যায়। স্বামীজি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন বলে দেশের সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। দেশ বলতে কী বুঝি? রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘দেশ মাটি দিয়ে গড়া নয়, মানুষ দিয়ে গড়া’। এই উপলব্ধি আমারও। দেশ মানে শুধু ভূখণ্ড নয়, তার ধারকবাহক তো দেশেরই অংশ। সামগ্রিক চেতনাই দেশকে অখণ্ডরূপে দেখতে সাহায্য করে। স্বদেশ চেতনা নিজের দেশকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর ‘মেবার পতন’ নাটকে স্বদেশ চেতনাকে সংকীর্ণতাদোেষ দুষ্ট বলে দেখিয়ে বিশ্বচেতনার জয় ঘোষণা করেছেন। এটা অবশ্য ঠিক যে ‘উদারচরিতানান্তু বসুবৈধ কুটুম্বকম্' অর্থাৎ উদারচরিত্রের মানুষদের কাছে বসুন্ধরাই কুটুম্বের মতো। বৃহৎ ভাবনা থেকে সরে এসে এ কথা বলা যায় যে, আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত ভারতভূমি আমার দেশ আর এদেশের মানুষ আমার ভাই, আমার প্রাণ।আমার চোখে আমার দেশ ভারতবর্ষ নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের দেশ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐকেই এদেশের বৈশিষ্ট্য। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ এদেশে বাস করে। অসামান্য প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এ দেশ। “কী বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়। আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। এর বিশাল নদনদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দামবেগে ছুটছে। এর মরুভূমি বিরাট স্বেচ্ছাচারের মতো তপ্ত বালিরাশি নিয়ে খেলা করছে।” ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকে সেকেন্দারের মুখে দ্বিজেন্দ্রলালের এই সংলাপই আমার চোখে আমার দেশ। আমার দেশের সনাতন সংস্কৃতি, সভ্যতা আমার আত্মা। এদেশের মানুষ আমার প্রাণের আত্মীয়। এদেশের ধূলিকণা সোনার চেয়ে দামি। এদেশ সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর দেশ, বহু মনীষীর আবির্ভাবে পুণ্য এ দেশ, এখানে যুগে যুগে অবতার মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। এ ভারতভূমি বিনয়-বাদল-দীনেশ, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী প্রমুখ শহিদের রক্তে রঞ্জিত। এদেশ বিদেশির কাছে ‘Tagore land’ নামে পরিচিত। পুণ্যসলিলা গঙ্গা এদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত।
এদেশের আকাশে-বাতাসে এদেশের মানুষের আনন্দধ্বনি ধ্বনিত হয়। এখন আমার দেশ পৃথিবীর বৃহত্তর গণতান্ত্রিক দেশ। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এদেশের শাসক বা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। সেই প্রতিনিধিদের উপর দেশের উন্নতি অগ্রগতি নির্ভর করে। কিন্তু বর্তমানে রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের অনুপ্রবেশ ঘটায় দেশের সম্পদ লুঠ হচ্ছে, ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে। দলমত নির্বিশেষে সবাই এক হতে না পারলে দেশ জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিতে পারবে না। আমার দেশের গরিমা অক্ষুণ্ন রেখে তার সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি করা আমাদের সকলের কর্তব্য। দিকে দিকে ন্যায়-নীতি আদর্শের অবক্ষয়, হিংসা, হানাহানি, মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন সামগ্রিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। সমস্ত নীতিবাচকতার ঊর্ধ্বে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে আমাদের স্বপ্নের দেশকে সাজিয়ে তোলার সংকল্প নিতে হবে। আমরা সকলে যেন কবিগুরুর সুরে সুর মিলিয়ে বলতে পারি—“সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে”।
আধুনিক জীবনে সংবাদপত্রের ভূমিকা
ロ আধুনিক জীবনে সংবাদপত্রের ভূমিকা সংবাদপত্র সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র। সংবাদপত্র আবার সমাজের জাগ্রত বিবেকও শব্দের সারিবদ্ধ মিছিলে বিশ্বের চলমান ঘটনাপ্রবাহের অনবদ্য গ্রন্থনা। আধুনিক মানুষের জীবন তাই সংবাদপত্রকে অসংকোচে তার সঙ্গী করে নিয়েছে। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে প্রথম সংবাদপত্রের অস্তিত্বের কথা জানা যায় বিভিন্ন সরকারি ঘোষণা ও নির্দেশনামায় যদিও সংবাদপত্রের আদিরূপ দেখা গিয়েছিল। প্রাচীন রোমে জুলিয়াস সিজারের এরকম বুলেটিনের কথা জানা যায়। ভারতে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত জেমস্ অগাস্টাস হিকি সম্পাদিত বেঙ্গলি গেজেটই প্রথম সংবাদপত্র হিসেবে চিহ্নিত এরপর ১৭৮৯ সালে প্রকাশিত হয় বোম্বে হেরল্ড। প্রথম বাংলা সংবাদপত্র হিসেবে ১৮১৮ সালের ২৩ মে প্রকাশিত হয় সমাচার দর্পণ। সংবাদপত্রের বিকাশের এই ইতিহাস সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। ২০০৭ সালে ভারতেই পাঁচ হাজার সংবাদপত্রের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। সমগ্র পৃথিবীতে রোজ ৩৯৫ মিলিয়ন সংবাদপত্র বিক্রি হয়, ভারতে এর পরিমাণ ৯৮.৮ মিলিয়ন। এইসব তথ্য আধুনিক জনজীবনে সংবাদপত্রের গ্রহণযোগ্যতারই প্রমাণ।বিভিন্ন দেশে বেশ কিছু সংবাদপত্র জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ইংল্যান্ডে দ্য টাইমস্, দ্য গার্ডিয়ানস্, দ্য অবসার্ভার ইত্যাদি কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্য নিউইয়র্ক টাইমস্, দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতে টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, দ্য স্টেটসম্যান, দ্য টেলিগ্রাফ, দ্য হিন্দু, হিন্দুস্থান টাইমস্ ইত্যাদি সংবাদপত্রের জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। বাংলায় আনন্দবাজার পত্রিকা, আজকাল, বর্তমান, সংবাদ প্রতিদিন ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। সংবাদপত্র হল গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। রাষ্ট্র পরিচালনায় সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য ফ্রান্সে একে ‘ফোর্থ এস্টেট’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সংবাদপত্র কোনো দেশের সরকার পরিচালন পদ্ধতিতে যেমন সতর্ক নজর রাখে, তেমনি রাষ্ট্রনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতির বিশ্লেষণ ও গঠনমূলক সমালোচনার মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে। পাঠকদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দিয়ে সরকার ও প্রশাসনের কাছে পৌঁছে দেয় জনগণের কণ্ঠস্বর। এইভাবে সংবাদপত্র হয়ে ওঠে গণতন্ত্রের সদাজাগ্রত প্রহরী। সংবাদপত্র বিনোদনেরও মাধ্যম। চলচ্চিত্র এবং খেলাধুলার বিস্তারিত খবর তুলে ধরে সংবাদপত্র। একজন কৃষকও তার কৃষি-সংক্রান্ত পরামর্শ পেয়ে যান সংবাদপত্র থেকে।
বিভিন্ন ক্ষেত্রে অচেনা নানা প্রতিভাকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসে সংবাদপত্র। শিক্ষার্থীদের জন্য নানা পরামর্শ ও পথ- নির্দেশনাও এর মাধ্যমে পাওয়া যায়। নানা ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মানুষদের তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণধর্মী লেখা পাঠকদের চিন্তার জগৎকে সমৃদ্ধ করে। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের সর্বগ্রাসী প্রভাব সংবাদপত্রকে কঠিন লড়াইয়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন অনলাইন সংবাদপত্র এই পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। তা সত্ত্বেও সংবাদপত্রের সর্বব্যাপী যে আবেদন—তা আজও অক্ষত। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সংবাদপত্র যেন তার গুরুত্বের অপব্যবহার না করে। কোনো বিশেষ স্বার্থের কাছে নিজেকে না বিকিয়ে দেয় সংবাদপত্রকে হতে হবে নিরপেক্ষ এবং সত্যনিষ্ঠ। তবেই তা জাতির জাগ্রত বিবেকের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠবে।
আধুনিক প্রযুক্তি ও আমরা
ロ আধুনিক প্রযুক্তি ও আমরা সভ্যতার ঊষাকালে মানুষের জীবন ছিল প্রতিকূলতা ও অনিশ্চয়তায় পূর্ণ। সেই কঠিন দিনযাপনকে ক্রমশ সহজ করে তোলে মানুষেরই মস্তিষ্কপ্রসূত নানান প্রয়োগকৌশল। কৃষিকাজ, আত্মরক্ষা, পশুশিকার, রান্নাবান্না প্রভৃতি ক্ষেত্রে লাঙল, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতির ব্যবহার তার জীবনে প্রযুক্তির প্রাথমিক সুফল এনে দেয়। আর প্রাচীনকালের সেইসব স্থূল প্রযুক্তির ক্রমোন্নয়নই আজ মানুষকে পৌঁছে দিয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের যুগে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সবকিছুতেই আজ জড়িয়ে রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞান। ইলেকট্রিক আলো পাখা, টেলিভিশন, রেডিয়ো, ফ্রিজ, হিটার, টেলিফোন, গ্যাস ওভেন প্রভৃতিতে তার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। বাইরে পা বাড়ালেও একই দৃশ্য ট্রেন, বাস, এরোপ্লেন, বড়ো বড়ো কলকারখানা থেকে শুরু করে জমিচাষের ট্রাক্টর, বীজ বপন ও ফসল কাটার মেশিন, ফসল ঝাড়াইয়ের মেশিন সবই প্রযুক্তিবিজ্ঞানের অবদান। সংবাদপত্র, রেডিয়ো, চলচ্চিত্র, দূরদর্শন প্রভৃতি গণমাধ্যম প্রযুক্তি বিজ্ঞানেরই অবদান। যত দিন যাচ্ছে ততই আরও উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এইসব গণমাধ্যম আরও বহু মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।
সংবাদপত্রের মুদ্রণ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে যুগান্তর এসেছে। উন্নত হয়েছে বেতার সম্প্রচার ব্যবস্থা আর টেলিভিশনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির বিস্ময়কর ব্যবহার সমগ্র বিশ্বকে এনে দিয়েছে আমাদের হাতের মুঠোয় মহাকাশ এবং পরমাণু গবেষণা— এই দুটি ক্ষেত্রে একালের বিজ্ঞানীদের আগ্রহ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। মহাকাশে স্থাপন করা হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহ, চন্দ্রে- মঙ্গলে-শুক্রে চলছে অভিযান, চলছে মহাকাশ সংক্রান্ত নানান গবেষণা। পরমাণুশক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন কাজে। কীভাবে এই শক্তিকে আরও বেশি করে কাজে লাগানো যায় তার জন্য বিজ্ঞানীদের চেষ্টার অন্ত নেই। আর এই প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রধান অবলম্বন প্রযুক্তিবিজ্ঞান। প্রযুক্তিবিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান কম্পিউটার। কম্পিউটারকে বাদ দিয়ে আধুনিক জীবনকে আজ ভাবাই যায় না। এই যন্ত্রটির সাহায্যে মানুষ ঘরে-বাইরে বহু জটিল ও দুরূহ কর্ম সম্পাদন করছে অত্যন্ত অল্প সময়ে। প্রযুক্তিবিজ্ঞানীদের অবিরাম চেষ্টায় দিন দিন এই যন্ত্রটি উন্নত হয়ে উঠছে। প্রযুক্তিবিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি মানবসভ্যতাকে বহুদূর এগিয়ে দিয়েছে। দ্রুততর হয়েছে সভ্যতার অগ্রগতি।
তবু মানুষের অশুভ বুদ্ধি এই প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অসামান্য শক্তিকে ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করতে দ্বিধা করছে না, যা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ তৈরি করছে ভয়ংকর মারণাস্ত্র। সেইসব মারণাস্ত্র প্রয়োগের আশঙ্কায় আজ সমগ্র পৃথিবী কাঁপছে। অন্যদিকে, কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে প্রযুক্তিবিজ্ঞানকে ব্যবহারের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্যও নষ্ট হতে বসেছে। অবিলম্বে সতর্ক না হলে চরম বিপদ ঘনিয়ে উঠতে আর বেশি দেরি নেই, মানবসভ্যতার বিনাশ তখন হবে কেবল সময়ের অপেক্ষামাত্র। আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞান আজ যে জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে তা মানবসভ্যতার চরম উৎকর্ষের প্রমাণ। মানুষ তার বুদ্ধি আর অধ্যবসায় দিয়ে এই অসাধ্যসাধন করেছে। তবে এই প্রযুক্তিবিজ্ঞান যাতে মানুষের এবং প্রকৃতির শত্রু না হয়ে উঠতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের তৎপর হতে হবে। শপথ নিতে হবে প্রযুক্তিবিজ্ঞানকে আমরা ব্যবহার করব শুধুমাত্র মানবকল্যাণেই।
অবকাশ যাপন
ロ “What is this life, if full of Care,
We have no time to stand and stare?"
-W.H. Davis
কর্মক্লান্ত মানুষ জীবনের অভ্যস্ত ধারাপাতে কিছুটা অবসর সন্ধান করে। অবসরের একান্ত মুহূর্ত আসলে জীবনের গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে নিজেকে নতুন করে খুঁজে পাওয়া। অবসর মুহূর্তে স্মৃতি রোমন্থনের মেদুরতায় মনের বিমুগ্ধ বিস্তার ঘটে আর তার মধ্যে দিয়েই খুঁজে নেওয়া যায় আগামীর প্রেরণা। অর্থ-যশ প্রতিষ্ঠার আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া মানুষেরজীবনে অবকাশ তাই ‘পরশপাথর’-এর মতো অতি আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। একটা সময় ছিল যখন মানুষের জীবন ছিল নির্ভার, নিশ্চয়তাপূর্ণ। কাজের অবসানে ছিল নিশ্চিন্ত অবসর। বাঙালি তখন সময় কাটাত চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায় সান্ধ্য মজলিশে।সেই অবসরযাপনে যেমন ছিল দাবা কিংবা পাশা খেলা, তেমনই পরনিন্দা-পরচর্চাও থাকত অনেকটা পরিসরজুড়ে। ক্রমশ
আটচালার স্থান দখল করে চায়ের দোকান, রেস্টুরেন্ট, খেলার মাঠ, থিয়েটার হল বা গানের জলসা। কিন্তু পেশাগত ব্যস্ততার ফাঁকে অবসরের সন্ধানে মানুষের চলা থেমে থাকেনি কখনও।
একুশ শতক, মানুষের সময়কে শাসন করার যুগ যন্ত্রসভ্যতার প্রবল দাবি মেনে মানুষও এখন যন্ত্রে রূপান্তরিত। পরিবর্তিত এই সময়ে ‘ডাকঘর’-এর অমল আর দইওয়ালার ডাক শুনতে পায় না, বরং ‘ছুটি’ গল্পের ফটিকের মতোই বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়—“এক বাঁও মেলে না, দো বাঁও মেলে না।” পেশাগত পরিধি যেমন এখন বহুধাবিস্তৃত, তেমনি ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক চাহিদাও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে, বিশ্বায়নের তীব্রতায় বিধবস্ত হয়ে পড়েছে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ, অনাবিল প্রশান্তি। আজকের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বারো ঘণ্টা কাজের জীবনে অবকাশ নেই, আর তাই হয়তো অবকাশের তাৎপর্য উপলব্ধ হয় আরও তীব্রভাবে। অবকাশ মানুষকে পেশাগত জীবনের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দেয়। বৈচিত্র্যের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয় তার জীবন। পরিশীলিত অবকাশযাপন সত্য ও সুন্দরের বোধে আস্থাশীল করে তোলে তাকে। ছাত্রদের জীবনে এই অবকাশ নিয়ে আসতে পারে মুক্তির সোচ্চার উল্লাস।
একদিকে অবকাশের মুহূর্তে মানুষ যেমন তার দৈনন্দিন ছক ভেঙে নতুন কর্মপ্রবাহের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে পারে, তেমনি অন্যদিকে সংগ্রহ করে নিতে পারে তার পরবর্তী দিনগুলোর প্রেরণা। অবকাশের মুহূর্তে জন্ম নিতে পারে স্মরণীয় কবিতা, গান বা চিত্রকলা, আবার এই সময়েই সাক্ষরতা আন্দোলন, বিজ্ঞান চেতনা প্রসারে বিভিন্ন আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করা যায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, “সত্যকে খুব বড়ো করে ধ্যান করবার এবং উপলব্ধি করবার মতো মনের উদার অবকাশ প্রয়োজন।” অবকাশ আসলে একটি মধ্যবর্তী পর্ব—কাজের এক অধ্যায় থেকে অন্য অধ্যায়ে যাওয়ার জন্য নিজেকে আরও উপযোগী, শুদ্ধতর ও সঠিক করে তোলার উপযুক্ত সময়।
অবকাশ তাই একদিকে হালকা হাওয়ায় অবরুদ্ধ আবেগকে যেমন অবাধ করে দেওয়া, তেমনি অন্যদিকে জীবনকে আরও ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করারও সময় চলাই জীবন, থেমে থাকাই মৃত্যু। কিন্তু ক্ষণিকের বিরতিও প্রয়োজন, চলার রসদ সংগ্রহের জন্য। বুনো ফুলের গন্ধে, নদীর বুক থেকে ভেসে আসা ভাটিয়ালি সুরে, অ্যাকাডেমিতে চলতে থাকা বিমূর্ত চিত্রকলার তুলির পোঁচে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের হৃদয় নিংড়ানো শব্দমালায় কিংবা ‘মেঘে ঢাকা তারা’র পাহাড় কাঁপানো ‘আমি বাঁচতে চাই’ চিৎকারে যেভাবেই হোক না কেন মানুষ খুঁজে নেয় অবসরের মণিমাণিক্য বেঁচে থাকারই তাগিদে।
ロ বর্তমান যুগ যন্ত্রসভ্যতার যুগ। মানুষ আজ বিজ্ঞানের তত্ত্বকে আয়ত্ত করে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে বিজয় অভিযান চালিয়েছে। প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের জীবনযাত্রা ও তার প্রগতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। মানুষ ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য জীবকুল প্রকৃতির দানকে যেমনভাবে লাভ করেছে, তেমনভাবেই তারা গ্রহণ করেছে। মানুষের মধ্যে আছে অফুরন্ত মননশক্তি। আর তার জোরে মানুষ নিজেদের প্রয়োজনানুসারে তাকে নানাভাবে রূপান্তরিত করেছে। প্রাচীন যুগেও মানুষ প্রযুক্তিবিদ্যাকে আয়ত্ত করেছিল। আত্মরক্ষার হাতিয়ার তৈরি করেছিল স্থূল পাথর ও লোহা দিয়ে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানের আবিষ্কারলব্ধ তত্ত্বের সঙ্গে প্রযুক্তিবিদ্যার ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধিত হয়েছে। আধুনিক যুগে যন্ত্রই প্রযুক্তিবিদ্যার বাহন। বিজ্ঞানের আবিষ্কারলব্ধ তত্ত্ব ও প্রযুক্তিবিদ্যা পরস্পরের উপর নিবিড়ভাবে নির্ভরশীল। আধুনিক জীবনের নানা সমস্যার সমাধানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগই প্রযুক্তিবিদ্যা। প্রযুক্তির ব্যবহারে আধুনিক জীবনের অশেষ কল্যাণ সাধিত হচ্ছে।
আমাদের প্রাত্যহিক জীবন প্রযুক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে আছে। প্রযুক্তির দান বৈদ্যুতিক পাখা, আলো, দ্রুতগামী যানবাহন, টিভি, রেডিয়ো, রেফ্রিজারেটর, বৈদ্যুতিক হিটার প্রভৃতি ছাড়া দৈনন্দিন জীবন অচল। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে বাড়ছে খাদ্যের চাহিদা। সেই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হচ্ছে নানারকম অধিক ফলনশীল শস্য। শস্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ— ট্রাক্টর, বীজবপন ও ফসলকাটার মেশিন, ফসল ঝাড়াইয়ের মেশিন সবই বিজ্ঞানের তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তির অবদান। বর্তমানে প্রযুক্তিবিদ্যা ছাড়া আধুনিক সভ্যতা তথা আধুনিক জীবনের কথা ভাবাই যায় না। বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তির অসাধারণ উন্নতি ঘটেছে। সংবাদপত্র, টিভি, রেডিয়ো, সিনেমা প্রভৃতি গণমাধ্যম প্রযুক্তিবিজ্ঞানেরই দান। বিজ্ঞানের নানা তত্ত্বের সাহায্যে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এইসব গণমাধ্যম বহু মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। জনগণের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে সংবাদপত্র, টিভি, রেডিয়োকে আরও উন্নত করার চেষ্টা হচ্ছে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে। বর্তমান পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে টিভির মতো গণমাধ্যমের সাহায্যে।
বর্তমান জীবনে কম্পিউটারের ব্যবহার আশ্চর্যভাবে বেড়ে উঠেছে। প্রযুক্তির হাত ধরে কম্পিউটারের মাধ্যমে নানান খবর, প্রয়োজনীয় তথ্যভাণ্ডার পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কম্পিউটারের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আদানপ্রদানের মতো সবরকম তথ্য গচ্ছিত রাখাও সম্ভব হয়েছে। পরমাণু গবেষণায় প্রযুক্তি বিজ্ঞান উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। পারমাণবিক গবেষণায় ভারত আজ যথেষ্ট এগিয়ে। শুধু পারমাণবিক অস্ত্র নয়, পরমাণু শক্তিকে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, তা নিয়েও পরমাণু বিজ্ঞানীরা অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন। পরমাণু গবেষণায় প্রযুক্তির ব্যবহার করেই সাফল্য লাভ সম্ভব হচ্ছে। বর্তমান সময়ে মহাকাশ গবেষণায় বিজ্ঞানীদের প্রচণ্ড আগ্রহ বেড়েছে। মহাকাশে স্থাপিত হয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহ, মঙ্গলগ্রহে অভিযান চলছে, চলছে মহাকাশ বিষয়ক নানা গবেষণা। এসবই প্রযুক্তিকে অবলম্বন করেই সম্ভব হচ্ছে।
প্রত্যেক জিনিসেরই ভালোমন্দ দুটি দিক আছে। আজকের প্রযুক্তিবিদ্যাও এই দ্বিমুখী ক্রিয়াকলাপ থেকে মুক্ত নয়। তাই সামাজিক মানুষ হিসেবে প্রযুক্তিবিদ্যাকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। প্রযুক্তিকে ভালো বা মন্দ যে-কোনো কাজেই ব্যবহার করা যায়। মানুষের নৈতিক দায়দায়িত্ব থাকে। ফলে মানবসভ্যতার কল্যাণেই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে অগ্রসর হতে হবে। প্রযুক্তিবিদ্যাকে সামাজিক ও মানবকল্যাণকর করে তোলার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মদগর্বী রাষ্ট্রনায়কেরা বিজ্ঞানের শক্তিকে প্রযুক্তিবিদ্যার কাজে লাগিয়ে তার নাশকতা শক্তির স্বরূপ জানতে উদ্গ্রীব। ফলে প্রযুক্তি বিজ্ঞান যেমন আধুনিক মানবজীবনের কল্যাণ সাধন করেছে, তেমনি সে প্রকারান্তরে সভ্যতা ও সংস্কৃতির
ক্ষতিসাধনেও উন্মুখ। প্রযুক্তি ও আধুনিক জীবন একে অপরের পরিপূরক। আধুনিক জীবনে প্রযুক্তির অপরিহার্যতা অস্বীকার করা যায় না। তবে এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সময়ে লক্ষ রাখতে হবে। প্রযুক্তির উদ্ভব মানবকল্যাণের জন্য। কিন্তু তাকে ধ্বংসকার্যে নিয়োজিত করলে তা হবে মানবজাতির পক্ষে অভিশাপস্বরূপ।
ロ চলমানতাই জীবজগতের সহজাত প্রবৃত্তি বিশ্বপ্রকৃতির এই অমোঘ শাশ্বত নিয়ম মেনেই আবহমানকাল ধরে চলে আসছে ক্রমঅভিযোজন, পরিবর্তন ও অভিব্যক্তি। পুরাতনের বিদায়, নতুনের আবাহন—মানবসভ্যতার ইতিহাসে তারই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের নিরলস অবিচ্ছিন্ন অনুসন্ধান, গবেষণা, নব নব আবিষ্কার, জীবনজিজ্ঞাসা-কৌতূহল নিত্যনতুন সৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়ে চলছে কাল থেকে কালান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে। আদিম বন্যজীবন থেকে গোষ্ঠীজীবনে, সেখান থেকে দাস সমাজে, ক্রমে ক্রমে সামন্ত সমাজ, ধনতান্ত্রিক সমাজে অনুপ্রবেশ প্রমাণ করে চলমানতাই জীবনের ধর্ম। প্রাক্-শিল্পবিপ্লবের পৃথিবীর সঙ্গে শিল্পবিপ্লবোত্তর পৃথিবীর মধ্যে কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে সমগ্র মানবসমাজে। জীবনে রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, জীবনদর্শন, মূল্যবোধ কালের প্রবাহে অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আগামী কুড়ি-পঁচিশ বছরে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে, তা বলাবাহুল্য।
আগামী কুড়ি-পঁচিশ বছরে আর্থ-সমাজব্যবস্থায় আসবে বিশাল পরিবর্তন। বিশ্ব অর্থনীতিতে বিশ্বায়ন, তথ্যপ্রযুক্তির দুর্নিবার প্রয়োগ, তৃতীয় বিশ্বের জনবিস্ফোরণ পৃথিবীর বুকে নিয়ে আসবে এক সমস্যাবহুল সংকটময় সন্ধিক্ষণ। আশীর্বাদ ও অভিশাপ দুটোই থাকবে। কার পাল্লা বেশি ভারী হবে, তা একমাত্র আগামী পৃথিবীই বলতে পারবে। অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ যেভাবে তার আগ্রাসী থাবা বিস্তার করছে, তাতে তৃতীয় বিশ্বের অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়বে, সাম্রাজ্যবাদীদের অঙ্গুলি হেলনে এসব দেশ ক্ষতবিক্ষত হবে। তখনই ঝড় উঠবে আর্থ-সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের তাগিদে। আগামী কুড়ি-পঁচিশ বছরে পারিবারিক সমাজজীবনেও আসবে এক বিপুল পরি ।। সেই পরিবর্তনের সূচনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। একান্নবর্তী পরিবার সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ছে, গড়ে উঠছে নিউক্লিয়াস পরিবার। ধীরে ধীরে বৈবাহিক জীবনের স্থলাভিষিক্ত হবে ‘গেট টুগেদার লাইফ'। নারী-পুরুষের প্রেম-ভালোবাসার, রোমান্টিকতার সংজ্ঞা যাবে বদলে; আত্মিক মাধুর্যে নয়, ধনদৌলত-বিলাস দিয়ে গড়ে উঠবে সেই রোমান্টিকতা।
নারী-পুরুষের মধ্যে চলবে তীব্র প্রতিযোগিতা—‘অধিকার’-এর প্রশ্নে। সকল পেশায় নারীরাও পুরুষদের মতোই দাপিয়ে বেড়াবে। পুরুষশাসিত সমাজ ভেঙে পড়বে, গড়ে উঠবে নতুন সমাজ, যেখানে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। চিকিৎসাশাস্ত্রে আসবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। চিকিৎসায় প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ হবে ব্যাপকভাবে। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাবে। দেখা দেবে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সমস্যা—যা ইতিপূর্বেই আমেরিকা, জার্মানি, জাপান, চিন দেশে দেখা দিয়েছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের গৃহে ঠাঁই হবে না, তাদের ঠাঁই হবে নিজবাস থেকে বহু দূরে কোনো বৃদ্ধাশ্রমে। মা-বাবা-ভাই-বোন- আত্মীয়স্বজনের মধুর স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসা, মায়া, মমতার মাধুর্য হারিয়ে যাবে। শিক্ষাজগতে আসবে নতুন মাত্রা। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির স্থলাভিষিক্ত হবে নিজ গৃহ। সিডি-ই হবে শিক্ষালাভের মাধ্যম।
অভিজ্ঞ শিক্ষকের দ্বারা সচিত্র সিডি প্রকাশ পাবে, যা শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। যেতে হবে না স্কুলকলেজে, নিতে হবে না প্রাইভেট টিউশন। টিভি, ভিডিয়ো ইত্যাদি নেবে স্কুল-কলেজ প্রভৃতির স্থান। যন্ত্রপাতিই হবে শিক্ষার্থীর শিক্ষার মূল্যায়নের হাতিয়ার, দরকার হবে না কোনো শিক্ষক, পরীক্ষকের। তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি, তার প্রয়োগ সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এনে দেবে বৈঠকখানায়। ব্যাবসাবাণিজ্য-যোগাযোগ পরিবহণে, সাহিত্যসংস্কৃতিতে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ পৃথিবীকে দেবে বিস্তৃতি, গতি, উত্তরণ। মানুষের দৈহিক-মানসিক ভার যাবে কমে, যন্ত্রের শাসন হবে কায়েম। শুরু হবে বৃহৎ সংখ্যক মানুষের শক্তি ও দৈহিক ক্ষমতার অবক্ষয়, তারপর হয়তো আসবে জড়ত্ব। আগামী কুড়ি-পঁচিশ বছরে পরিবেশ কী অবস্থায় পৌঁছোবে, তা ভাবলে দুঃস্বপ্নের ভিড়ে রাতের ঘুম যাবে ছুটে।
পরিবেশসচেতন মানুষরা, বিজ্ঞানীরা এখন থেকেই প্রমাদ গুনতে শুরু করেছেন। যে হারে বাতাস-মাটি-জল-দূষিত হচ্ছে, গ্রিন হাউস ভেঙে পড়ছে, বাস্তুরীতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, ওজোনস্তর ভেদ করে মারাত্মক অতিবেগুনি রশ্মি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে, আছড়ে পড়ছে মেরুপ্রদেশে—তাতে করে আশঙ্কা জাগছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুর্লভ জীবজগতের ধ্বংস কি আরও অনিবার্য হয়ে উঠবে না? আগামী কুড়ি-পঁচিশ বছরেই হয়তো তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। মানুষ চেতনশীল, মননশীল। চরম বিপত্তির আভাস পেয়ে আগামী পৃথিবীকে রক্ষা করতে সমস্ত শ্রেণির মানুষ এগিয়ে আসবে। টেনে দেবে বল্গাহীন বিজ্ঞানের অগ্রগতির রশিকে। ধ্বংসের পথে নয়; শুধু সৃষ্টির পথে, কল্যাণের পথে মানুষের চিন্তাভাবনা বিজ্ঞানের প্রয়োগকেই স্বীকৃতি দেবে। মানুষের মধ্য থেকেই সেই শুভ চেতনা জেগে উঠবে আগামী দিনে, এই প্রত্যাশা নিয়ে প্রহর গুনতে থাকব—আমরা পৃথিবীর মানুষ।
আমি যদি পাখি হতাম
ロ ছেলেবেলা থেকে যত বার জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছি, মনে হয়েছে ততবার আমি যদি পাখি হতাম! যদি পাখি হয়ে ডানা মেলতে পারতাম ওই সুদূর নীলাকাশে, যদি গাছে গাছে ফল খেয়ে বেড়াতে পারতাম, তাহলে কত মজাই না হত। এই অপ্রতিরোধ্য মুক্ত জীবনের উল্লাসে গা ভাসানোর আনন্দই আমার পাখি হয়ে জন্মাতে চাওয়ার অন্যতম কারণ। নিজেকে নির্দিষ্ট সীমার ঊর্ধ্বে সুদূর উচ্চতায় কে না মেলে ধরতে চায়? আমিও তার ব্যতিক্রম নই। যদি আমি পাখি হতাম তাহলে নিজের মতো করে সবার আগে কোনো গাছের ডালে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রকৃতির নানা উপাদান এবং ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তুলতাম সাধের নীড়। সময়ে-অসময়ে প্রকৃতির এলোমেলো হাওয়ায় দোদুল্যমান বাসায় বসে সমাজের দোলাচলকে উপলব্ধি করতাম। নির্বিকার চিত্তে ছড়িয়ে থাকা খড়কুটো সংগ্রহের মধ্য দিয়ে নিজের সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতাম। উপলব্ধি করতে পারতাম পৃথিবীতে কোনো জিনিসই মূল্যহীন নয়।
কালের পরিপ্রেক্ষিতে, স্থানের নির্বাচনে ও সঠিক প্রচেষ্টায় সকল দ্রব্যেরই একটি মূল্য আছে, কোনো কিছুই ফেলে দেওয়ার নয়। পাখি হয়ে জন্মালে শহুরে জীবনযন্ত্রণা হয়তো আমাকে দগ্ধ করবে; গগনচুম্বী বহুতল নির্মাণের পরিমাণ বৃদ্ধি, হোটেল কিংবা শপিংমল নির্মাণের জন্য বৃক্ষচ্ছেদ কিংবা মোবাইল টাওয়ারের অত্যাচারে হয়তো আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে ঠিকই—কিন্তু তবু এই বাংলার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মধ্যে আমি শুনতে চাই এক চিরন্তনী হৃৎস্পন্দন। তাই বাংলার কবি জীবনানন্দের প্রতিধ্বনি করে সুর তুলতে ইচ্ছা হয় এই বলে—“হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে/কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়...' পাখি হয়ে জন্মানোর মধ্যে আমি ফিরে পেতে চাই আমার অস্তিত্বকে, পালন করতে চাই আমার সামাজিক দায়িত্বকেও।
প্রতিদিন ভোরবেলায় আমার কুজনে প্রাণীকুলের ঘুম ভাঙবে। আমার মধুর কণ্ঠধ্বনিতে এক সৌন্দর্যময় ধ্যানমগ্ন আত্মার আবাহন ঘটবে। অজস্র ফুটে ওঠা কোকনদের মধ্য দিয়ে আমি মানবতার বার্তা পৌঁছে দেব ঘরে ঘরে। 'Strangeness added to beauty'-র মায়া-অঞ্জন চোখে মেখে যে স্বপ্নের নীড় আমি রচনা করতে চাই; সেখানে থাকবে না কোনো সাম্প্রদায়িকতা, প্রতিহিংসা বা বিচ্ছেদের কালো ছায়া। থাকবে শুধু ভালোবাসা, সমৃদ্ধি আর প্রশান্তি। আমি হতে চাই এক দুরন্ত পাখি। চিড়িয়াখানা বা খাঁচার নির্দিষ্ট গণ্ডিতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না আমি। আমার মধ্যে থাকবে সীমা থেকে অসীমে যাওয়ার ব্যাপ্তি। কোনো ভৌগোলিক সীমারেখায় আমাকে আবদ্ধ করা যাবে না। আমি হয়ে উঠতে চাই কখনও বিশ্ব শান্তির প্রতীক, কখনও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রতীক, কখনও বা মানবতার বার্তাবাহী। তাই আমি হব এক এবং অদ্বিতীয়। আমাকে নিয়ে শিল্পী ছবি আঁকবেন নতুন চেতনায় । আমাকে নিয়ে কবি কবিতা লিখবেন নতুন ভাবনায়; আমাকে নিয়ে গীতিকার সুর সংযোজন করবেন নতুন মূর্ছনায়। জন্মজন্মান্তর ধরে শিল্পসৃষ্টির মধ্যেই আমি চিরায়ত থাকব। আমার কায়িক মৃত্যু ঘটলেও আমার আত্মিক অস্তিত্ব থাকবে সর্বজনের হৃদয় মাঝারে।
আজ যখন দেখি সমাজে মানুষ তার শ্রেষ্ঠ গুণগুলিকে বিসর্জন দিয়ে নানান মতভেদ, জাতিভেদ, বর্ণভেদ, কুসংস্কারকে লালনপালন করছে সযত্নে; তখনই বারবার মনে হয় আমি যদি পাখি হতাম তাহলে অন্তত আমার চোখে সবকিছু সমান লাগত। কারণ উচ্চতা থেকে সকল কিছুকেই সমান লাগে উচ্চতা সকল ভেদকেই ঘুচিয়ে একীভূত করে প্রতিষ্ঠিত করে সাম্য।
ロ সময় প্রবহমান; আর তার সঙ্গে সংগতি রেখে সভ্যতা, সংস্কৃতি, চিন্তাভাবনা সবই পরিবর্তিত হয়। সেই পরিবর্তনের ধারাকে মেনে সভ্যতা অগ্রসর হয়। শৈশবে আমার চারপাশের পরিবেশে ছিল আকাশ, সূর্য, নক্ষত্র, চাঁদ, গাছপালা, মুক্ত বাতাস। এই ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে আমার প্রতিবেশী ও সামাজিক পরিবেশ মিলিত হওয়ার ফলে আমার পক্ষে অজানাকে জানা ও অচেনাকে চেনা সম্ভব হয়েছে। শৈশবে সন্ধ্যার সময় বাড়ির দাওয়ায় বসে পূর্ণিমার আকাশে পূর্ণ চাঁদ দেখতাম আর শুভ্র জ্যোৎস্নায় চারদিকের পরিবেশ আমার মনকে পুলকিত করে তুলত। ঠাকুরমা আকাশের পূর্ণ চাঁদ দেখিয়ে বলত, ‘ঐ দ্যাখ খোকা চাঁদ!’ আমি প্রশ্ন করতাম চাঁদের মধ্যে ওটা কীসের ছায়া গো ঠাকুরমা? ঠাকুরমা বলতেন, ‘আরে ওটাই তো চাঁদের বুড়ি। দেখছিস না চাঁদের মধ্যে এক মনে চরকা কেটে চলেছে।' আমি অবাক হয়ে যেতাম। ঠাকুরমা বলতেন—“চাঁদের বুড়ি চাঁদের বুড়ি মর্ত্যে আস নামি।” চাঁদের বুড়ি বলত—“কাজ ফেলে তোমার কাছে কেমনে আসব নামি।”
ঠাকুরমার সেই গল্পকথা এবং রূপকথা আমার মনে আনন্দের সঞ্চার করত। এইসব রূপকথার গল্প শুনে আমার মন কল্পনার জগতে বিরাজ করত। এরপর ছেলেবেলায় আমাদের গ্রামে যখনই পূর্ণিমার রাতে আকাশের দিকে চেয়ে চাঁদকে দেখতাম, তখনই যেন শুনতে পেতাম চাঁদের মধ্যে সেই বুড়ি যেন আমাকে বলছে—“আমার কাছে চলে আয়, তাহলে অনেক অজানাকে জানতে পারবি, অচেনাকে চিনতে পারবি।” তারপর ধীরে ধীরে বড়ো হয়েছি, জেনেছি চাঁদের মধ্যে সেই ছায়া চাঁদের বুড়ি নয়। ওই ছায়া আসলে চাঁদের মধ্যে যে পাহাড়-পর্বত রয়েছে, তার ছায়া। কিন্তু এসব জানা সত্ত্বেও পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে দেখে মনে হত সেখানে সত্যিই চাঁদের বুড়ি রয়েছে।
আজকের যুগের শিশুরা কিন্তু চাঁদের বুড়ির কথা জানে না। বর্তমানে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার ও যান্ত্রিকতা পরিপূর্ণ জীবনে শিশুর শৈশব হারিয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফলে একান্নবর্তী পরিবারের পরিবর্তে ছোটো ছোটো পরিবারে সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একান্নবর্তী পরিবারে ঠাকুরমা ও ঠাকুরদার ভূমিকা নেই বললেই চলে। আজকের শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে তাদের শৈশবের কল্পনার জগৎ থেকে, রূপকথার জগৎ থেকে। তারা জানে না রূপকথার কাহিনি। তারা ঠাকুরমার মুখে শোনে না কল্পনার গল্প, রূপকথার গল্প। তাদের জীবনের প্রথম শিক্ষা ঠাকুরমা ও ঠাকুরদার কাছে হয় না। শৈশবে শিশুদের আর শেখানো হয় না—
“আয় আয় চাঁদমামা টি দিয়ে যা
আমার খোকনের কপালে টি দিয়ে যা।”
দু-বছর বয়স থেকে শিশুকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে পাঁচিলে ঘেরা অচলায়তনের মধ্যে। সেখানে নিয়ম ও আচারের মধ্যে তাদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা হয়। তাদের কল্পনাজগৎকে, ভাবনার জগৎকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। আর শিক্ষার জাঁতাকলে পড়ে তারা ভুলে যায় তাদের শৈশব বলে কিছু আছে। আর এই কারণে তারা জানতে পারে না আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্যের কথা। যার মধ্যে রয়েছে কল্পনার জগৎ।
আজকের শিশুরা একাকী থাকে বলে তাদের জ্ঞানের জগৎ কম্পিউটার গেম্স আর টিভির কার্টুনেই সীমাবদ্ধ। অবাস্তব সব ভয়ংকর, রোমাঞ্চকর এবং হত্যা ও নৃশংস কাহিনির মধ্যে তাদের অবসর অতিবাহিত হয়। তাদের মনের মধ্যে পুরোনো রূপকথার গল্প কল্পজগতের গল্পের কোনো রেশ থাকে না। তারা জানে না রাজপুত্র-রাজকন্যার গল্প, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির গল্প। আকাশের নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য দেখিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। তারা জানে না পূর্ণিমার রাতের চাঁদ দেখতে কেমন। তাদের কল্পনাশক্তিকে বিকশিত করার কেউ নেই। তাদের বিচরণ শুধু কম্পিউটার, ট্যাব, মোবাইলের জগতে। কল্পনার জগৎ বলতে তারা শুধু বোঝে হ্যারি পটার কিংবা স্পাইডারম্যান। শিশুদের মন শৈশবেই হারিয়ে যায়।
সভ্যতার বিকাশের ফলে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের স্বাভাবিক জগৎ। প্রকৃতি, পরিবেশ, অরণ্য, জলাভূমি সব হারিয়ে যাচ্ছে। সেই সব জায়গায় গড়ে উঠছে ইট, পাথরের জঙ্গল। বৈদ্যুতিক আলোর ঝলকানিতে আকাশের চাঁদের আলো আজ ম্লান। কবির (অশোক বিজয় রাহা) ভাষায় সত্যিই— "আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে!” শিশুর স্বাভাবিক আকর্ষণ তাই আর আকাশের চাঁদের প্রতি থাকে না। সে লক্ষ করে না চাঁদকে, আর তাই ‘চাঁদের বুড়ি’ থেকে যায় গল্প হয়েই; শৈশবের অংশ হতে পারে না।
ロ বৈষম্যমূলক আর্থসামাজিক ব্যবস্থা সভ্যতার সিঁড়ি বেয়ে আমরা যত অগ্রগতির উচ্চ শিখরে উঠছি ততই আমাদের সমাজজীবনে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। সেই জটিলতার ছিদ্রপথেই সমাজে প্রবেশ করছে নানা অন্যায়-অপরাধমূলক কাজ। আদিম সাম্যভোগবাদী সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পর থেকে মানুষের সমাজজীবনে ঘটে চলেছে নানা পরিবর্তন। ব্যক্তি সম্পত্তির উদ্ভব, উৎপাদন ব্যবস্থার নানা কাঠামো ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন, উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ, উদ্বৃত্ত উৎপাদন, উৎপাদনের উপকরণের মালিকানার পরিবর্তন, শিল্প-কলকারখানায় কৃষিতে ভাড়া করা শ্রমিক নিয়োগ, ব্যাবসাবাণিজ্যের আন্তর্জাতিকতা, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ প্রভৃতির চরিত্র পরিবর্তনে বর্তমান সমাজে সৃষ্টি হয়েছে চার শ্রেণির মানুষ আর্থসমাজ দৃষ্টিভঙ্গিতে—ধনী, উচ্চমধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণি।
একদিকে মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণি অন্যদিকে অগণিত দরিদ্র শ্রেণির মানুষ। একদিকে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী শোষক সম্প্রদায়, অন্যদিকে সংখ্যাতীত বঞ্চিত শোষিত নির্যাতিত মানুষ। একদিকে ভোগবিলাসের প্রাচুর্য, আর একদিকে অনাহারে-অর্ধাহারে অপুষ্টিক্লিষ্ট মানুষের দীনতা। এই বৈষম্যমূলক সমাজে দেখা দিয়েছে তাই নানা ব্যাধি-চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, খুনখারাপি কার্যকলাপ। অথচ কোনো মানুষই চোর-ডাকাত খুনি হয়ে জন্মায় না। কঠিন-কঠোর বাস্তব সমাজজীবন তাদের সেসব পথে ঠেলে দেয়। যেদিন থেকে আর্যসমাজ ব্যবস্থায় এই অবক্ষয় শুরু হয়েছে তবে থেকেই এই অন্যায়-অপরাধমূলক কাজ ঘটে আসছে এবং তা আরও তীব্র মাত্রা লাভ করছে। আর এই অন্যায়-অপরাধ দমন করার জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা তৎপর হয়ে উঠেছে। তাই গড়ে উঠেছে আইন-আদালত প্রশাসন। আইনের চোখে চোর দোষী, তার শাস্তি হয় আইনমাফিক।
পরের দ্রব্য অপহরণ করাই হল চুরি এবং তা অন্যায় ও অপরাধ। আইনের চোখে চোর অপরাধী ও শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু চোর কেন চুরি করল, সেটাও আমাদের জানতে হবে। নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে যদি অভাবের তাড়নায় কেউ চুরি করতে বাধ্য হয়, তবে তা অপরাধ কি না তা বিচার করার সময় এসেছে। দিনান্ত পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও যখন একজন দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সংস্থান করতে পারে না, রোগে ছেলে-মেয়ে-বউ-এর চিকিৎসা করতে পারে না, চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায় ও বিনা পথ্যে আপনজনকে মৃত্যু মুখে ঢলে পড়তে দেখে; তখন যদি কোনো ব্যক্তি স্নেহ-ভালোবাসা-মায়া-মমতার টানে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও চুরি করে অনাহারক্লিষ্ট স্বজনের মুখে গ্রাস তুলে দিতে, রোগের চিকিৎসা করাতে; তখন কি তা খুবই অমানবিক, অন্যায়, অপরাধ? যখন একজন মানুষ লেখাপড়া শিখে কাজের জন্য হন্যে হয়েও বেকার থাকতে বাধ্য হয়, জঠর যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চুরি করতে বাধ্য হয়, তখন কি তা অমার্জনীয়? সংবেদনশীল দৃষ্টি মেলে অনুসন্ধান করব না—কেন চুরি করে? কোথায় তার উৎস বৈষম্যমূলক আর্থসমাজব্যবস্থার মধ্যে অপরাধমূলক কাজের বিষবীজ উপ্ত রয়েছে।
সমাজের একশ্রেণির মানুষ কম আয়াসেই ভোগবিলাসের আতিশয্যে বংশপরম্পরায় জীবন অতিবাহিত করেছে, আর-এক বৃহৎ শ্রেণির মানুষ অক্লান্ত পরিশ্রম করেও ন্যূনতম অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে না। যেসকল কৃপণ যক্ষের মতো ধনদৌলত আগলে রেখেছে; যারা সমাজে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে নিজস্বার্থ সিদ্ধ করছে, সে সকল ব্যক্তিই সমাজের ভাগ্যনির্ধারক। তারাই সমাজের প্রভাবশালী, তারাই সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তির ভাবমূর্তি হয়ে বিরাজ করে, এদেরই কারণে সমাজে এত অভাব-অনটন, এত বেকার, এত অন্যায়-অবিচার-অপরাধ। অথচ আইনের চোখে এরা নিরপরাধ। এরাই কৌশলে আইন-আদালত-প্রশাসনকে কুক্ষিগত করে শ্রমজীবী-কৃষক-শ্রমিক-মজদুর শ্রেণির মানুষের মুখের গ্রাস, পরিধানের বস্ত্র মাথা গোঁজার ঠাঁই কেড়ে নিয়েছে। এদেরই কারণে সমাজে এত অন্যায়-অবিচার-অপরাধ ঘটে। যতদিন সমাজে এই ব্যবস্থা, এই কৃপণ ধনী থাকবে; ততদিন সমাজে চোর চুরি করবে, ডাকাত ডাকাতি করবে, খুনি খুন করবে।
বস্তুত আর্থসমাজব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করার সময় এসেছে। চোর দোষী; কিন্তু তদপেক্ষা শত গুণ দোষী কৃপণ ধনী, যাদের কারণে সমাজে চোর-ডাকাত-খুনির জন্ম হয়। চোর-ডাকাত-খুনি হয়ে কেউ জন্মায় না। সমাজব্যবস্থাই মানুষকে সৎ, মহৎ ও সমবেদনশীল করে তুলতে পারে; আবার সেই সমাজই মানুষকে চোর-ডাকাত-খুনিও করতে পারে। বৈষম্যমূলক আর্থসমাজ ভেঙে সাম্যবাদী আর্থসমাজব্যবস্থা গড়ে উঠলে মানবসমাজ অনেক সমস্যা ও অন্যায়-অবিচার-অপরাধ থেকে মুক্ত হতে পারবে। তাই আইন-আদালতের শাসনব্যবস্থায় গড়ে উঠুক সুস্থ স্বাভাবিক উন্নত সমাজব্যবস্থা, যার ভিত্তি হবে—মানবতা, সততা ও সমবেদনশীলতা।
ロ গতানুগতিক জীবনধারায় কর্মক্লান্ত মানুষ সন্ধান করে কিছুটা অবসর। যদিও জীবনসংগ্রামে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে কর্মই একমাত্র অবলম্বন তবুও মানুষ তার চেনা ছকের বাইরে গিয়ে প্রাকৃতিক জগতের মায়াময় রূপের আকর্ষণে কর্মজগৎ থেকে অবকাশ পেতে চায়। এই অবকাশ মানুষের জীবনের শান্তি-তৃপ্তি ও আনন্দের আহ্বায়ক। অবকাশের মধ্য দিয়েই মানুষ হয়তো তার নতুন কর্ম-উদ্যমতা খুঁজে পায়। জীবনকে সুন্দর ও বৈচিত্র্যময় করে তুলতে অবকাশ মানুষের কাছে ‘পরশপাথর’স্বরূপ। অবকাশ বলতে সাধারণ অর্থে বিরতি বোঝায়। শহরের দৈনন্দিন জীবনের নিশ্ছিদ্র অবসরহীন কর্মপ্রবাহে আমরা বিকেলে পৃথিবীর রং ফেরা দেখি না, একা আপন মনের মুখোমুখি হই না। তার জন্য প্রয়োজন ছুটি, দৈনন্দিন জীবনের কর্মপ্রবাহ থেকে ছুটি।
মানুষ এই অবকাশের জন্য জীবনকে উপভোগ করতে পারে। কর্ম মানুষের পেটের ক্ষুধা মেটায়, অবকাশ দূর করে মানুষের মনের ক্ষুধা। মনই চালক, অবকাশ চালকের শক্তি। একটা সময় ছিল যখন মানুষের জীবন ছিল নিশ্চয়তাপূর্ণ। কাজের অবসানের পর মানুষের হাতে থাকত অগাধ সময় এবং তা অবসর বিনোদনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হত। বাঙালি তখন সময় কাটাত চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায় সান্ধ্য মজলিশে। সেই অবসরযাপনে যেমন তাস খেলা, পাশা খেলা থাকত তেমনই থাকত পরনিন্দা-পরচর্চার মতো মনোরঞ্জনকারী উপাদান। ক্রমশ আটচালার যুগের অবসান হয়, বাঙালি তখন ভিড় জমাতে শুরু করে চায়ের দোকানে, কফিহাউসে, খেলার মাঠে, থিয়েটার হলে কিংবা গানের জলসায়। তারপর পৃথিবীটা আরও ছোটো হতে হতে ড্রয়িংরুমের বোকাবাক্সতে বন্দি হল, সেলফোন আর ইনটারনেটে অভ্যস্ত অমলকান্তিরা আর রোদ্দুর হতে পারে না।
কর্মব্যস্ত ‘অন্ধকার’ ঘরেই আজকের কর্মচঞ্চল অমলকান্তিদের দিনপাত হয়। অবকাশহীন জীবন তাদের করে তোলে দুর্বিষহ। কিন্তু তাদের মন সব সময় মুক্তি পেতে চায়, শান্তি পেতে চায় নরম রোদ্দুরে। কলুর বলদ হয়ে বেঁচে থাকার পরিবর্তে বৈচিত্র্যময় জীবনের অংশীদার হতে চায় সে। বৈচিত্র্যের সঞ্জীবনী সুধায় মনকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। সত্য আর সুন্দরের বোধ পরিশোধিত হয়ে ওঠে অবসর যাপনের মধ্য দিয়েই। অবকাশ মুহূর্তে মানুষ যেমন একদিকে দৈনন্দিনতার ছক ভেঙে নতুন কর্মপ্রবাহের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে পারে, অন্যদিকে এখান থেকেই সে সংগ্রহ করে নিতে পারে তার পরবর্তী দিনগুলির প্রেরণা।
আর এই সময়ই মানুষ হয়ে ওঠে সৃজনশীল চিন্তাকে চেতনায়, ভাবনাকে কর্মে আর কল্পনাকে বাস্তবে রূপদানের সলতে পাকানোর কাজটি শুরু হয় এই অবসর পর্বেই। তাই গান শুনে, সাহিত্যে মনোনিবেশ করে, ছবি আঁকায় মন দিয়ে কিংবা অন্যকিছু করে মানুষ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মেতে ওঠে। অবসর মানেই মুক্ত বিহঙ্গের অনুভূতি, এক মুক্তির আনন্দ। ধরা
বাঁধা জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিজের মতো করে চলা বা কিছু করা। নিজেকে নিজের মতো করে পাওয়া। কর্মব্যস্ত জীবন চাওয়াপাওয়ার মধ্যে যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, অবসর যাপনই পারে সেই প্রতিবন্ধকতা জয় করতে। অবকাশ জীবনে নিয়ে আসে মুক্তির আনন্দ, জীবনধারণের সঞ্জীবনীসুধা। তাই প্রতিটি মানুষের জীবনে প্রয়োজন পর্যাপ্ত অবকাশ।



.png)